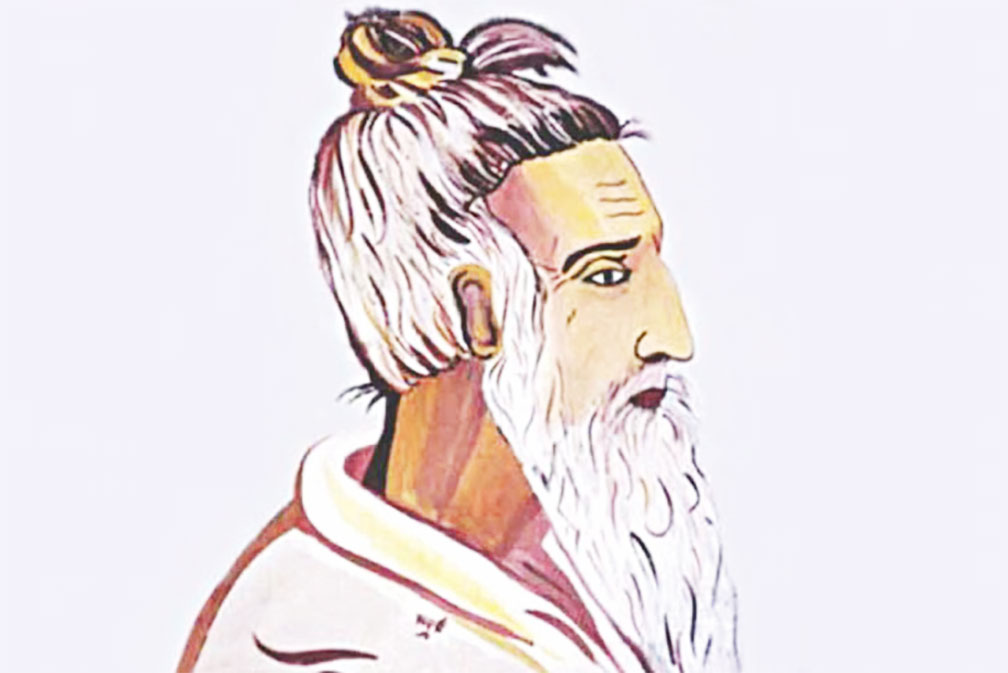বিশাল এক রহস্য মানুষ বা প্রাণীকুলের জন্ম এবং মৃত্যু!
নিশ্চয়
মনে প্রশ্ন ওঠে, কেন জনম? কেন মৃত্যু? জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যখানে যে জীবনের
অপরূপ রূপকথা-সেই রূপকথার ঘোরে অজস্র মানুষ পথ হারিয়েছেন, পথে পথ খুঁজতে
খুঁজতে। অজস্র প্রজ্ঞাবান মানুষের মনে উদিত এই প্রশ্নের সমাধানও অমীমাংসিত।
কিন্তু মানুষ নিজেও কম রহস্যময় নয়। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ চিন্তাশীল
স্রোতের দিকে যেমন সাঁতার কাটে, কেউ কেউ উল্টোদিকেও সাঁতার কেটে, অভেদের
ভেদ রহস্য উন্মোচনে নিজেকে উৎসর্গ করে।
মহাত্মা লালন ফকির আমৃত্যু ভেদ ও
অভেদের মধ্যে বিরাজিত রহস্যের সন্ধানে ব্যাপৃত থেকেছেন। তিনি ছিলেন জীবনের
পাঠশালার চিরকালের শিক্ষার্থী। একই সঙ্গে সমাজের সব স‚ত্র ধারণ করে
এগিয়েছেন। তিনি বহুমাত্রিক ধ্যান- ধারণায় বিকশিত সৃষ্টি রহস্যের সন্ধানের
মধ্যে মানুষের মনের আলোর কণাও খুঁজে পেয়েছেন। সৃষ্টি ও মানুষ-পরস্পর সহজিয়া
ঘরানার সম্পর্কের সঙ্গে সমাজ বাস্তবতার রূপরেখার অনুসন্ধানের ব্যাপৃত
ছিলেন আমৃত্যু।
গানেই তিনি ব্যক্ত করেছেন নিজের আকিঞ্চন-
‘জাত গেল জাত গেল বলে
একি আজব কারখানা।
সত্য কাজে কেউ নয় রাজি
সবই দেখি তা না না না।।
..............................
গোপনে যে বেশ্যার ভাত খায়
তাতে ধর্মের কী ক্ষতি হয়।
লালন বলে জাত কারে কয়
এই ভ্রম তো গেল না।।’
তিনি
জাতি ধর্ম বর্ণ- সবাইকে মানুষ ভেবেছেন। মানুষের মধ্যে কোনো জাত পাত থাকতে
পারে না। সব ধর্ম কর্ম ও রঙের মানুষ মিলে একটি মহাজাতি। মানব জাতির মধ্যে
নানা ধরনের মত পার্থক্য থাকতে পারে, থাকাটাই স্বাভাবিক কিন্তু কেউ কাউকে
ঘৃণা বা অপমান করুন, মহাত্মা লালন চাননি। তিনি সব মানুষের মধ্যে নিবিড়
মানবিক সম্পর্কের সৌধ রচনা করতে চেয়েছেন।
লালন ফকির কত সালে জন্ম গ্রহণ
করেছেন, এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করে তথ্য পাওয়া যায় না। লালন সম্পর্কে প্রথম
জীবনী পুস্তক রচনা করেছিলেন বসন্তকুমার পাল [১৮৯০- ১৯৭৫]। তিনি ১৯৫৫ সালে
রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথের সহায়তায় মহাত্মা লালন ফকির প্রকাশ করেন।
তিনি লালনের জন্ম ও জীবনের প্রকাশ সম্পর্কে লেখেন-“লালনের জন্ম সাবেক
নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত কুমারখালী থানার চাপড়া-ভাঁড়ারা
গ্রামে হিন্দু কায়স্থকুলে। বাল্যনাম লালন কর। পিতার নাম- মাধবচন্দ্র কর।...
শৈশবে লালন পিতৃহীন হন। যৌবনের প্রথমে বিবাহকার্য সমাপ্তের কিছুদিন পর
প্রতিবেশী বাউল দাসের সঙ্গে তিনি নৌকায় মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে যান
গঙ্গাস্নানে।
ফেরার পথে আক্রান্ত হন বসন্ত রোগে। রোগের প্রকোপে এক সময়ে
বাহ্যচেতনা লুপ্ত হলে তাঁকে সঙ্গীরা মৃত্যু ভেবে যথাবিহিত
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে মুখাগ্নি করে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে চলে যান
সঙ্গীরা। গ্রামে ফিরে এসে সঙ্গীরা লালনরে জননী, স্ত্রীসহ অন্যান্য আত্মীয়
স্বজনকে জানায় বসন্তরোগে লালনের মৃত্যু হয়েছে। এবং গঙ্গায় নিক্ষেপ করা
হয়েছে।
এদিকে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া জ্ঞানহীন লালনের দেহ ভাসতে ভাসতে ঠেকে
একটা ঘাটে। সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে এক তন্তুবায় মুসলিম মহিলা ঘাটে এসে
দেখে মৃতপ্রায় লালনকে। অনেকের সহযোগিতায় মহিলা লালনকে নিয়ে যায় বাড়িতে। ওই
মহিলার সেবাযতেœ লালন আরোগ্যলাভ করে গ্রামে ফিরে গেলে জননী ও স্ত্রী তাকে
দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলেও সগোত্র থেকে ঘোরতর আপত্তি ওঠে সমাজে স্থান
দেওয়া নিয়ে। যেহেতু লালনের অন্ত্যেষ্টি- শ্রাদ্ধাদি ইত্যাদি আচার অনুষ্ঠান
সম্পন্ন হয়েছে, কাজেই প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া তাকে থাকতে হবে- ‘আপন মায়ের ঘরে
পরের ছেলে’ হয়ে।
কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা মানা
সংসারের অভাব অনটনের কারণে লালন-জননীর পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না। অপরদিকে
আত্মীয়স্বজন ও সগোত্র-সমাজের চাপে একদিন কলাপাতায় জননী পরিবেশিত অন্নগ্রহণ
করে বিক্ষুব্ধ হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যান লালন।
বসন্ত রোগে অসুস্থ হয়ে লালন
যখন মুসলিম তন্তুবায় মহিলার বয়নগৃহে ছিলেন, ওই সময় সেখানে এসেছিলেন যশোর
জেলার ফুলবাড়ি গ্রামের সিরাজ সাঁই নামে এক সাধক ফকির। তন্তুবায় মুসলিম
মহিলার সেবাযতেœর পাশাপাশি লালনকে সিরাজ সাঁই কবিরাজি প্রক্রিয়ায় চিকিৎসা
করেন। সিরাজের মরমি উপদেশে লালনের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় এক নতুন চেতনার আবেশ।
এবার তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে সিরাজ সাঁইয়ের কাছে এসে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে
শুরু করেন সাধক জীবন। গুরু সিরাজ সাঁইয়ের মৃত্যুর পর তিনি ছেঁউড়িয়ায় এসে
আখড়া স্থাপন করে সেখানেই বসবাস করেন আমৃত্যু।”
জীবনের অভিজ্ঞতায় লালনের
মনের মধ্যে উদিত প্রশ্ন-মানুষ কী? মানুষ কেন? মানুষ যদি মানুষই হয়, তাহলে
এত দেয়াল কেন ধর্মের? তিনি অন্তরচক্ষু উন্মীলিত করে মানুষের মধ্যে যে দয়াময়
মানুষ বাস করে, সেই দুর্ভেদ্যে সংবেদ সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন।
সাধনার
মধ্য দিয়ে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মহামানব আত্মার সমুদ্রে অবগাহন করতে
থাকেন। যে অমৃত তিনি অনুধাবন করেন, তারই আলোকে গানের পশরা সাজান-
‘...সুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারীলোকের কি হয় বিধান।
বামন চিনি পৈতে প্রমাণ
বামনী চিনি কি করে।।
কেউ মালা কেউ তসবিহ গলে
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলে।
আসা কিংবা যাওয়ার কালে
জাতের চিহ্ন রয় কারে।।
জগৎ জুড়ে জাতের কথা
লোকে গল্প করে যথাতথা।
লালন বলে জাতের ফাতা
ডুবাইছি সাধবাজারে।।’
গানের
কথায় তিনি প্রমাণ করেছেন-পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর প্রতি যে বৈষম্য রচনা
করা হয়েছে, সেই বৈষম্য নারী ও পুরুষ ভেদে নানা স্তরে ছড়িয়ে গেছে। এখানে
মানুষ মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। তিনি সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে উঠে মানবিক সমাজের
নবায়ন করতে চেয়েছিলেন।
তার ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে যথেষ্ট
মতভেদ আছে, সেটা এখনো যেমন, জীবিত থাকার সময়েও ছিল। লালনের মৃত্যুর পর
প্রথম জীবনীকার বসন্তকুমার লিখেছেন-‘সাঁইজি হিন্দু কি মুসলমান এ কথা স্থির
করতে আমিও অক্ষম। নানা স‚ত্র থেকে জানা যায়, মহাত্মা লালন সাঁই জীবদ্দশায়
কোনো ধর্ম পালন করেননি। তাঁর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না কিন্তু জীবন
ও মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, হিন্দু মুসলমানদের ধর্মের ভেতর ও বাইরের
বিষয়ে শাস্ত্র থেকে নিজেই আহরণ করেছেন। মুসলমানদের সঙ্গে লালনের চমৎকার
যোগাযোগ, ওঠা বসার কারণে অনেকে মুসলমান মনে করেছে। বিপরীতে বৈষ্ণব ধর্মের
আলোচনা করতে দেখে হিন্দুরা মনে করতেন, লালন বৈষ্ণব।’
প্রকৃতপক্ষে লালন ছিলেন মানবতাবাদী। তিনি জাত, ধর্ম, ক‚ল, বর্ণ, লিঙ্গ অনুসারে মতভেদে বিশ্বাস করতেন না।
বিশিষ্ট
লোক গবেষক সুধীর চক্রবর্তী একটা লেখায় লালন সম্পর্কে লিখেছেন-‘কাঙ্গাল
হরিনাথ তাকে জানতেন, মীর মশাররফ তাকে চিনতেন, ঠাকুরদের হাউসবোডে যাতায়াত
ছিল, লেখক জলধর সেন ও অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় তাকে কতোবার সামনাসামনি দেখেছেন
কতোবার- গান শুনেছেন, তবুও জানতে পারেন নি লালনের জাত পরিচয়, বংশধারা বা
ধর্ম।’
ধারণা করা যায়, লালন রোগাক্রান্ত হয়ে মুসলমান পরিবারে আশ্রয়
পেয়ে, মুসলমানদের সেবায় সুস্থ হয়ে উঠলে নিজ ধর্মের লোক কর্তৃক নিপীড়নের
শিকার হয়েছিলেন। যা কেউ কোথাও কৌশলগত কারণে উল্লেখ করেননি। এই ধর্মের কারণে
মানুষ বাধা নিষেধের বেড়াজাল সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে বিভেদের দেয়াল
সৃষ্টি করে, লালন এই দেয়াল মেনে নিতে পারেননি।
ফলে তিনি নিজের বোধ
বিবেচনা এবং মরমী জীবনের গভীর অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে নতুন জীবন ও জীবন
দর্শনের চর্চা করেছেন। সেই জীবন লৌকিক জীবন, সব মানুষ নিয়ে প্রশ্ন ও দ্বিধা
ছাড়া এক পিড়িতে বসে মানব দর্শনই সেই জীবনের পরম আখড়া বিবেচনা করেছেন।
তিনি গানে মানবজনমের অক্ষম অপচয়ের জন্য আক্ষেপ রচনা করেছেন-
‘এমন মানব জনম আর কি হবে।
মন যা কর ত্বরায় কর এই ভবে।।
অনন্ত রূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবরূপের উত্তম কিছুই নাই।
দেব দেবতাগণ করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে।।’
ভাবা
যায়, লালন মানব জীবনকে কতটা গভীর বোধ ও অন্তপুরের চেতনা থেকে উপলব্ধি
করেছেন, লিখেছেন-দেব দেবতাগণ করে আরাধন/জন্ম নিতে মানবে...। দেবতারা মানুষ
হওয়ার জন্য আরাধনা করছে। অথচ সেই মানব জীবন আমরা কত সহজেই পেয়েছি কিন্তু
জনমের কোনো সার্থকতা লিপিবদ্ধ করতে পারিনি, এই মানব জীবনে।
লালনের গানে
মানবিকতা, কালিক ভাবনা, অসাম্প্রদায়িকতা ও সমাজ বাস্তবতার যে চিন্তা চেতনার
সাক্ষাৎ মেলে, সেই চিন্তা চেতনা বিশ্বমানবিক ম‚ল্যবোধেরই পরিচয় বহন করে।
লালনের গুরুত্বপ‚র্ণ অবদান কেবল বাঙালি মরমি কবিদের সারিতে কিংবা গীতি
কবিদের সীমায় সীমিত নয় বরং বিশ্ব লোকসংস্কৃতির অঙ্গনেও সাড়া তুলেছে
তুমুলভাবে।
লেখক: কথাসাহিত্যিক