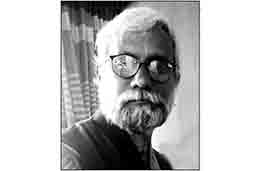
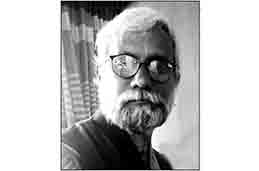
নজরুলের সংগীত প্রতিভা নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। এই ভুবনে তিনি কালজয়ী স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা গানের রস-গ্রহীতাদের জন্য নব-প্রেরণার উৎস এবং তৃপ্তিস্থল ছিল নজরুলের বিষয় বৈচিত্র্যের গান। অনেকে মনে করেন, গ্রামোফোন কোম্পানির খপ্পরে পড়ে নজরুলের কাব্য সাধনা ক্ষদিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু কবির সৃজন প্রতিভা জননন্দিত ও কালান্তরকে অতিক্রম করা প্রমাণ করে, নজরুল নজরুলই থেকে গেছেন। যা হবার তিনি তাই হয়েছে। এটাই তাঁর নিয়তি। মানুষের অন্তরের সহজ সরল আবেদন ছিল নজরুলের গানের ভাষায়। যে বুঝে এবং যে বুঝে না সুরের রাগ-বৈচিত্র্য , তারও হৃদয়ের ভাষা হতে পেরেছে নজরুল সংগীত। যার জন্যে সকল শ্রেণির মানুষের কাছে নজরুল সংগীত আদৃত হয়েছে । তাঁর গান মানুষের ভালবাসা অর্জনে সক্ষম হবে এই আত্মবিশ্বাস ছিল বলেই নজরুল ‘জনসাহিত্য সংসদ’ নামে একটি সংস্থার অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন,
‘কাব্য ও সাহিত্যে আমি কী দিয়েছি, জানি না। আমার আবেগে যা এসেছিল তাই আমি সহজভাবে বলেছি।
আমি যা অনুভব করেছি তাই আমি বলেছি। ওতে আমার কৃত্রিমতা ছিল না। কিন্তু সংগীতে যা দিয়েছি,
সে সম্বন্ধে আজ কোন আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে তখন আমার
কথা সবাই স্মরণ করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। সাহিত্যে দান আমার কতটুকু তা আমার জানা নেই।
তবে এইটুকু মনে আছে, সংগীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি।’-(উদ্ধতি : অরুণ বসু, কলকাতা, ২০০০ : ৪৩০)
সংগীতে ‘কিছু দিতে পারার আত্মপ্রত্যয়’ কাজী নজরুল ইসলামের নিস্ফল ছিল না। শতাব্দী ধরে বাংলা গানের উৎকর্ষের বিচারে পাঁচজন সংগীতজ্ঞের মধ্যে যে দু’টি নাম সবার আগে উচ্চারিত হয় তাঁদের একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এবং অন্যজন কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) । বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ বয়োজ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) ও অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪) এঁদের সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের পার্থক্য গোড়া থেকেই।নজরুল এঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। অগ্রজ রবি ঠাকুরের মতো তিনিও মূলত কবি এবং সংগীত-সাধক ছিলেন। সাধনার ফলেই তিনি হতে পেরেছেন কালজয়ী সংগীতের বাণী-শিল্পী, সুরকার, সংগীত-পরিচালক ও রাগ-সংগীতেরও স্রষ্টা ।
কাব্য এবং সংগীতে নজরুলের সামগ্রিক প্রেমচেতনা সর্বস্তরের মানুষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। কবির কাবাঘর, মন্দির, গির্জা মানুষের হৃদয়। নজরুলের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী উপমহাদেশের ধর্মীয় বিভেদকে সচেতনভাবে অগ্রাহ্য করেছে। বাংলা গজল রচনার সময় ফার্সি গজলের মূলভাব প্রেমকে অবলম্বন করে নজরুল অদ্বৈতবাদী সত্তার বন্দনা করেছেন এটাই নজরুলের ধর্মচেতনার মূল সুর। প্রার্থনায়, নিজেকে নিবেদনে সকল ধর্মের সাধক, প্রেমিক ও সাধারণ মানুষকে এক করে দেখেছেন।
নজরুলের কলমে ফার্সি গজলের মূলভাব ঐশী প্রেমকে কেন্দ্র করে প্রথম বাংলা গজল রচিত হয়েছে। স্ফূর্তি লাভ করেছে পরমাত্মার আনন্দে। এই সমস্ত গজলের হৃদয় হচ্ছে সেই পাত্র, যে পাত্রে ঠাঁই পাওয়ার একমাত্র যোগ্যতা নিবিড় প্রেম । সাধক নজরুলের মানবিক প্রেম জাগতিক সম্পর্ককে ছাড়িয়ে জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রেমে রূপ নিয়েছে। লক্ষ করি, যে প্রেম আসে ঘুমঘোরে। ঘুম ভেঙে বিচ্ছেদ রূপ নেয় কান্নায়। নজরুলের একটি বিখ্যাত বাংলা গজলে প্রেমিক বলেন :
মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর
নমো নম, নমো নম, নমো নম।...
শিয়রে বসি চুপি চুপি চুমিলে নয়ন
মোর বিকশিল আবেশে তনু
নীপ-সম, নিরুপম, মনোরম ।।...
স্বপনে কী যে কয়েছি তাই গিয়াছ চলি,
জাগিয়া কেঁদে ডাকি দেবতায়-
প্রিয়তম প্রিয়তম প্রিয়তম।। (সংক্ষেপিত)
জানা আছে, ফার্সি গজল রচয়িতা ইরানি কবিরা ছিলেন মরমী । মনের ভাব প্রকাশে ফুল, পাখি, শরাব, সাকি, কুঞ্জবন ইত্যাদি উপমা ব্যবহার করে লৌকিক জগত ছাড়িয়ে লোকোত্তর জগতের দ্যেতনা সৃষ্টি করাই গজলের মূল উদ্যেশ্য । যেখানে থাকে অদ্বৈত পরমসত্তা বা পরমাত্মার সঙ্গে জীবত্মার বিরহ-মিলনের অপরোক্ষ অনুভবের বাণী। অতীন্দ্রিয় স্বপ্নসুখ। মাটিতে এর জন্ম, কিন্তু দৃষ্টি আকাশে। যার বিস্তৃতি গভীর ব্যঞ্জনাময়। নজরুল এই প্রেমধর্মকে মনেপ্রাণে বরণ করেছেন। প্রেমে সাধক বা প্রেমিকের কোন ভেদ নেই। জাত নেই । সে একই সত্তার প্রেমিক, অনন্ত বিরহের মধ্যে থাকে এবং তাঁর মিলনও তাই বিরহেরই নামান্তর। কেননা, মিলনের পরেই বিচ্ছেদ। পরমাত্মার পরশ যখন জীবাত্মা পায়, তখন মিলনে আনন্দ পায়। আবার একই সঙ্গে বিরহের আশঙ্কায় তার মন বেদনায় কাঁদে, চোখ জলে ভরে ওঠে । বুকের এই তৃষ্ণা সাত-সাগরের জলেও মিটে না । এই ভাবের প্রচুর জনপ্রিয় গজল নজরুলের ভাণ্ডারে আছে। রয়েছে। যেমন :
এক.
কেন কাঁদে পরান কী বেদনায় কারে কহি।
সদা কাঁপে ভীরু হিয়া রহি রহি ।।
সে থাকে নীল নভে আমি নয়ন-জল-সায়রে...
কাজল করি যারে রাখি গো আঁখি-পাতে,
স্বপনে যায় সে ধুয়ে গোপন অশ্রু-সাথে।। (সংক্ষেপিত)
দুই.
এত জল ও- কাজল চোখে
পাষাণী, আনলে বলো কে।
টলমল জল-মোতির মালা
দুলিছে ঝালর-পলকে।।...
বুকে তোর সাত সাগরের জল,
পিপাসা মিটল না কবি
ফটিক-জল! জল খুঁজিস যেথায়
কেবলি তড়িৎ ঝলকে।। (সংক্ষেপিত)
তিন.
নহে নহে প্রিয়, এ নয় আঁখি-জল
মলিন হয়েছে ঘুমে চোখের কাজল।। (সংক্ষেপিত)
চার.
কি হবে জানিয়া বলো
কেন জল নয়নে
তুমি তো ঘুমায়ে আছো
সুখে ফুল-শয়নে।।
তুমি কি বুঝিবে বালা
কুসুমে কীটের জ্বালা,
কারো গলে দোলে মালা
কেহ ঝরে পবনে।। (সংক্ষেপিত)
এই সমস্ত গজলের প্রেমিক, সাধকের প্রেমপাত্র চিরকালের অধরা, অচেনা, অজানা । প্রেমিকা রাধা তাঁকে চোখে দেখতে পায় না, শুধু বাঁশি শুনতে পায়। নজরুলের যাকে ‘বিদেশী’ বলে সেই অনন্ত সত্তা, পরমাত্মাকেই বুঝিয়েছেন । যিনি বাঁশিতে সুর তুলে জীবাত্মাকে ডাক দেন। সে ঘুমের ঘোরে জেগে ওঠে এবং সেই বাঁশির সুরে তার হিয়া কাঁদে,
কে বিদেশী বন-উদাসী বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে ।।
সুর-সোহাগে তন্দ্রা লাগে কুসুম-বাগের গুল্-বদনে ।।...
সহসা জাগি আধেক রাতে
শুনি সে বাঁশি বাজে হিয়াতে
বাহু- শিথানে কেন কে জানে
কাঁদে গো বাঁশির সনে ।। (সংক্ষেপিত)
প্রকৃতি অনুসারে নজরুল তাঁর গজলে লোকায়ত ঐতিহ্যের চিরকালের নায়ক-নায়িকা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকেই মানবিক রূপ দিয়েছেন। রূপকের আড়ালে তিনি প্রেমিকের প্রতি প্রেমাষ্পদের, পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার, মাশুকের প্রতি আশেকের, স্রষ্টার প্রতি সাধকের বিরহী আত্মার ক্রন্দনকে সহজ মানবিক ভাষায় রূপ দিয়েছেন। সংগীতের বাণীর এই সরলতার গুণের জন্য নজরুলের প্রেমানুভব সারা বাংলার মৃত্তিকা সংলগ্ন মানুষ, শহুরে মানুষ, শিক্ষিত হৃদয় সকলের মন জয় করে নিয়েছিল। এই শ্রেণির সংগীতে নজরুল ঈর্ষণীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর তুলনা কেবল তিনি নিজে। এই ধারার আরও কয়েকটি সংগীত,
এক,
বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
পানিয়া ভরণে চলে লো গোরি।-
চলে জলে চল কাঁদে বনতল
ডাকে ছলছল জল লহরী ।। (সংক্ষেপিত)
দুই.
নিশি ভোর হল জাগিয়া, পরান-পিয়া ।
কাঁদে ‘পিউ কাঁহা পাপিয়া, পরান-পিয়া ।।...
জেগে রয় জাগায় সাথি- দূরে চাঁদ, শিয়রে বাতি,
কাঁদি ফুল-শয়ন পাতিয়া, পরান পিয়া ।। (সংক্ষেপিত)
তিন.
কেমনে রাখি আঁখিবারি চাপিয়া
প্রাতে কোকিল কাঁদে, নিশিথে পাপিয়া ।।
এ ভরা ভাদরে আমার মরা নদী
উথলি উথলি উঠিছে নিরবধি!
আমার এ ভাঙা-ঘটে
আমার এ হৃদি তটে
দুকূল ছাপিয়া ।। (সংক্ষেপিত)
উপর্যুক্ত গজল সমূহের সারা অবয়ব জুড়ে কেবল না-পাওয়া অপেক্ষার কান্না । বেদনায় শুধু যে প্রেমিক কাঁদে তা না, প্রকৃতিও কাঁদে। প্রাতে কোকিল কাঁদে, নিশীথে পাপিয়া।
নজরুলের বাংলা গজলে প্রেমিকের, সাধকের যে রূপ ইসলামি গান, ভক্তিগীতিতেও একই। এখানেও প্রেমাবেদন তীব্র অনুরাগের, অনুভবের। নিজের সত্তাকে পরমাত্মায় বিলীন করে দিয়ে সৃষ্টিতে মিশে এক হয়ে যেতে চেয়েছেন । সুফিবাদীরা যাকে বলেছেন, ফানা ফিল্লাহ’। অদ্বৈতসত্তার সাথে বিলীন হয়ে যাওয়া । মিলনের এমন নিবিড় অনুভব নজরুলের ইসলামি সংগীতে আছে । যেমন :
ধূলিকণা হবো, আমি ধূলিকণা হবো
(ওগো) নবী পদরেখা যেই পথে আঁকা
সেই পথে বিছাইবৃ
পথমুখো হয়ে কদম রসুল
চুম দিবো অনুরাগে।
ধূলি হ’বো, আমি সেই পথের ওই ধূলি হ’বো
নবী যে পথ দিয়ে চলেছিলেন। -(সংক্ষেপিত)
প্রেমাস্পদ এখানে সৃষ্টিতে মিশে ধূলিকণা হয়ে প্রেমিকের সান্নিধ্যে পেতে চাইছে। যে পথ দিয়ে প্রেমিক গেছেন সেই পথের ধূলিকণা হতে চাইছেন নবী-প্রেমিক নজরুল। তাঁর আধুনিক গানেও আছে এমন অনুভবের আবীর। যে অনুরাগের চিত্র ভিন্নদৃষ্টিতে দেখার অবকাশ আছে। যেখানে ব্যক্তি সত্তা নৈর্ব্যক্তিক রূপ পেয়েছে। সাধকের দেহ এবং মন যখন প্রকৃতির সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায় তখন তার ভিতরে ঝরণা প্রবাহিত হয়। প্রাণ-অপ্রাণ ও প্রকৃতিতে কোন পার্থক্য থাকে না। চিতা বাঘ মিতা হয়ে যায়। গোখরোর মতো বিষধর সাপ হয় খেলার সাথি।তাই মনের আনন্দে সাপের ঝাঁপি বুকে নিয়ে সুখে রাত কাটানো তখন অসম্ভব হয় না,
আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ / ঐ পাহাড়ের ঝরণা আমি উধাও হয়ে বই গো
উধাও হয়ে বই।।/ চিতা বাঘ মিতা আমার গোখরো খেলার সাথী
সাপের ঝাপি বুকে করে সুখে কাটাই রাতি / ঘূর্ণি হাওয়ার উর্ণি ধরে
নাচি তা থৈ থৈ ।। (সংক্ষেপিত)
বস্তুত ইসলামি সংগীত রচনার সময়েও নজরুলের অদ্বৈতবাদী প্রেম-চেতনা তাঁকে সার্বজনীন প্রেম-চেতনায় স্থিত রেখেছে। এ কারণে তাঁর ইসলামি সংগীত যে-কোন ধর্মের প্রেমিকের ভাবসম্পদ। ইসলাম ধর্মে বর্ণিত স্রষ্টা ‘আল্লাহ’কে নজরুল প্রভু, এবং নিজেকে ভৃত্য না ভেবে সুফীদের মতো প্রেমিক ভেবেছেন। তাই খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকেন। যে-পথে তাঁর মুর্শিদ নবী মোহাম্মদ আসবেন। আর এই নবী মোহাম্মদের নাম যাঁর হৃদয়ে আছে তাঁর সাথে খোদারও আছে গোপন পরিচয়। সুফিদের মতো নবীকে তিনি মুর্শিদ রূপে অন্তরে ধারণ করেছেন। যিনি খোদার সাথে প্রেমের সম্পর্কের মাধ্যম। এমন অনুভবের ইসলামি সংগীত নজরুলের নাথ’এ স্পষ্ট,
১.
খোদার প্রেমে শরাব পিয়ে বেহুঁশ হয়ে রই পড়ে
ছেড়ে’ মসজিদ আমার মুর্শিদ এলো যে এই পথ ধরে (হায়) (সংক্ষেপিত)
২.
আমার মোহাম্মদের নামের ধেয়ান হৃদয়ে যার রয়
ওগো হৃদয়ে যার রয়।
খোদার সাথে হয়েছে তার গোপন পরিচয়।। (সংক্ষেপিত)
নজরুল বিশ্বাস করেন, ইসলামের মহানবীকে নজরুল স্রষ্টা কেবল মুসলিমদের জন্য প্রেরণ করেননি। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দ) শুধু মুসলমানদের জন্য প্রেরিত হননি। তিনি মুসলিম অমুসলিম, মানবজাতির মুক্তির জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। উঁচু-নিচু, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ ভেদ না করে সাম্যের বাণী প্রচার করে গেছেন। তিনি মানবজাতির মহামিলনের, প্রেমের বাণী উচ্চারণ করেছেন যা এযুগের মানুষ বিস্মৃত হয়েছে। নজরুল রচিত দুটি ইসলামি সংগীতের অংশবিশেষ, যেমন :
১.
লহ সালাম লহ, দ্বীনের বাদশাহ, জয় আখেরে নবী
পীড়িত জনগণে মুক্তি দিতে এলে হে নবীকুলের রবি।।
তুমি আসার আগে ধরার মজলুম
করিত ফরিয়াদ, চোখে ছিল না ঘুম,
ধরার জিন্দানে, বন্দী ইনসানে আজাদি দিতে এলে হে প্রিয় আল-আরাবি ।। (সংক্ষেপিত)
২.
তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ ক্ষমা কর হযরত।
মোরা ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ, তোমারি দেখানো পথ ।।...
প্রভু তোমার ধর্মে অবিশ্বাসীরে তুমি ঘৃণা না’হি করে
আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাঁই দিয়ে নিজ ঘরে।...
তুমি চাহ নাই ধর্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি,
তলোয়ার তুমি দাও নাই হাতে, দিয়াছ অমর বাণী।
মোরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা
সার করিয়াছি ধর্মান্ধতা,
বেহেশত হ’তে ঝরে নকো আর তাই তব রহমত।। (সংক্ষেপিত)
কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামি সংগীতে নবিপ্রেমের গানের সংখ্যা বেশি। মহানবিকে তিনি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ত্রিভুবন’র মোহাম্মদ (দ) বলে একাধিক সংগীতে অভিষিক্ত করেছেন। আচার-নিষ্ঠ ইসলামি ভাষ্যকাররা এই চেতনা কখনো সমর্থন করেন না। তাঁরা বেহেস্ত-দোজখ, ইহকাল-পরকাল ধারণা প্রচার করেন। মানেন। কিন্তু সুফিবাদী প্রেমিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নজরুল নবী মোহাম্মদকে ‘ত্রিভুবন’র প্রিয় নিখিলের প্রেমাষ্পদ বলে বন্দনা করেছেন । এই দুটি ইসলামি-সংগীতে বিষয়টি স্পষ্ট। যেমন :
১.
ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়
আয়রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয় ।।...
আজকে যত পাপী ও তাপী, সব গুনাহের পেল মাফী
দুনিয়া হতে বেইনসাফী জুলুম নিল বিদায় ।। (সংক্ষেপিত)
২.
বারেক মুখে নিলে যাঁহার নাম, চিরতরে হয় দোজখ হারাম,
পাপীর তরে দস্তে যাঁহার কাওসারের পিয়ালা।।
‘মিম’ হরফ না থাকলে সে আহাদ, নামে মাখা তাঁর শিরিন শাহাদ,
নিখিল প্রেমাষ্পদ আমার মোহাম্মদ ত্রিভুবন উজালা।।
আল্লাহকে পাওয়ার জন্য মুর্শিদ ভাবনা, নবীকে ভালবাসে স্রষ্টার নৈকট্য লাভের প্রয়াস, মোহাম্মদ (দ) নাম জপমালা করা, নবীকে মধ্যস্থতাকারী মানা দ্বৈতবাদী ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিক নয়। কিন্তু অদ্বৈত সুফিবাদী প্রেমিক, সাধক, আউলিয়া, দরবেশ নবীপ্রেমিকদের মতো নজরুলও বিশ্বাস করেন আল্লাহকে পেতে হলে নবিকে ভালবেসেই পেতে হবে। মূল ইসলামের সঙ্গে সুফিবাদী প্রেমিকদের এখানে বড় ব্যবধান। পীর-মুর্শিদের মাধ্যমে তাঁরা সৃষ্টিকর্তাকে পেতে চান। যেমন, নজরুল সংগীতের বাণী,
১,
‘আল্লাহকে যে পাইতে চাহে, হযরতকে ভালোবেসে’।
আরশ কুরসি লওহ কালাম, না চাহিতেই পেয়েছে সে ।। (সংক্ষেপিত)
২.
তৌহিদেরই মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম।
ঐ নাম জপলেই বুঝতে পারি খোদায়ী কালাম-
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম ।। (সংক্ষেপিত)
৩.
মোহাম্মদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে।
তাই কিরে তোর কণ্ঠেরি গান, ওরে এমন মধুর লাগে।।
ওরে গোলাপ নিরিবিলি
নবীর কদম ছুঁয়েছিলি-
তাঁর কদমের খোশবু আজো তোর আতরে জাগে।। (সংক্ষেপিত)
৪.
ওরে ও দরিয়ার মাঝি! মোরে নিয়ে যা রে মদিনা।
তুমি মুর্শিদ হয় পথ দেখাও ভাই আমি যে পথ চিনি না।।
আমার প্রিয় হযরত সেথায়
আছেন নাকি ঘুমিয়ে ভাই,
আমি প্রালে যে আর বাঁচি না রে আমার হজরতের দরশ বিনা।। (সংক্ষেপিত)
প্রেমধর্মে বিশ্বাসী নজরুল তাঁর সমগ্র সৃষ্টিতে যেকোন বিভেদকে অস্বীকার করেছেন। প্রতিবেশী ধর্মের ভক্তিগীতি রচনার ক্ষেত্রেও নজরুল অভেদ চেতনার পরিচয় দিয়েছেন । সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মের অনুসারী হয়েও বৈষ্ণব ও শাক্তসংগীত রচনার দক্ষতা নজরুল ব্যতীত আর কেউ দেখাতে পারেননি। নজরুলের কৃতিত্ব এই যে, শ্যাম-শ্যামা ভক্তদের মধ্যে যে-বিরোধ, তাকে আমলে না নিয়ে প্রেমিকের দৃষ্টিতে তিনি শ্যামা মায়ের কোলে শ্যামকে বসিয়ে দিয়েছেন। শ্যাম সংগীতের কৃষ্ণপ্রেম, শ্যামা সংগীতে মাতৃরূপে উপাসকের বন্দনা এবং ভক্তিমূলক গানে নজরুলের অদ্বৈত প্রেমভাব, দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে মিলনের, সমন্বয়ের।
সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা মুসলিমদের আল্লাহ এবং তাঁর প্রেরিত রসুল ইসলামের মহানবীকে সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে ব্যাপ্ত তাঁদের অস্তিত্ব বুঝাতে নজরুল ইসলামি সংগীতে ত্রিভূবন’ ব্যবহার করেছেন। সেই একই অর্থে ভক্তিমূলক গানে, শ্যাম-শ্যামা সংগীতেও তিনি ‘ত্রিভুবন’ ‘ত্রিজগত’ ‘ত্রিলোক’, ত্রিনয়ন’, ত্রিলোচন’, ত্রিশূল’ ইত্যাদি রূপক শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থে কোন ভিন্নতা নেই । এক্ষেত্রে নজরুল মহামিলনের মোহনায় দাঁড়িয়ে আছেন ত্রিজগত আলো করে যার দ্যুতি আছে এই সমস্ত ভক্তিমূলক গানে,
শ্যামা সংগীতে :
১.
আশ্রয় মোর নাই জননী ত্রিভুবনে কোথাও হায়!
দাঁড়াই মাগো কাহার কাছে তুইও যদি ঠেলিস পায়! (সংক্ষেপিত)
২.
ত্রিজগত আলো করে আছে কালো মেয়ের পায়ের শোভা
মহাভাবে বিভোর শঙ্কর, ঐ পা জড়িয়ে মনোলোভা ।।...
ঐ চরণ শোভা দেখার তরে, যোগী থাকেন ধেয়ান ধ’রে।
ত্রিভুবন ভুলে অনন্তকাল যোগী থাকেন ধেয়ান ধ’রে। (সংক্ষেপিত)
শ্যাম সংগীতে :
১.
তুমি রাজা, নহ শুধু দ্বারকার,
ত্রিলোকের রাজা তুমি সম্রাট গ্রহ রবি শশি তারকার।।
ছিলে রাজা মথুরায়, রাজা ব্রজধামে
শ্যাম, রাজা ছিলে তুমি কিশোরী বামে।
তুমি বনে রাজা, তুমি মনে রাজা
শিশু নটরাজ তুমি কোলে যশোদার।। (সংক্ষেপিত)
ভক্তিমূলক গানে :
১.
মৌন আরতি তব বাজে নিশিদিন
ত্রিভুবন মাঝে প্রভু বাণী-বিহীণ ।।...
ধ্যান-মৌনী মহাযোগী অটল
আপন মহিমায় তুমি সমাসীন।। (সংক্ষেপিত)
২.
ব্যথিত প্রাণে দানো শান্তি, চিরন্তন, ধ্রুব-জ্যোতি।
দুখ-তাপ-পীড়িত-শোকার্ত এই যাচে তব সান্ত্বনা ত্রিভুবন-পতি। (সংক্ষেপিত)
৩.
প্রভাত বীণা তব বাজে হে
উদার অম্বর মাঝে হে।।
তুষার কান্তি তব প্রশান্তি
শুভ্র আলোকে রাজে হে।।
তব আনন্দিত গভীর বাণী
শোনে ত্রিভুবন যুক্ত পাণি
মন্ত্রমুগ্ধ ভাব গঙ্গা নিস্তরঙ্গা লাজে হে’।। (সংক্ষেপিত)
একই ধর্মের মধ্যে ব্যাখ্যা কিংবা মতের ভিন্নতা হিন্দু-মুসলামান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে। ইসলাম ধর্মে শিয়া. সুন্নি, কুর্দি, হানাফি, সোহরোওয়ার্দি ইত্যাদি নানা মত ও পথ যেমন আছে, তেমনি হিন্দুদের মধ্যেও শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, ব্রাহ্ম এদের মধ্যে প্রভেদ আছে। হিন্দু ধর্মের মধ্যে উনিশ শতকে কালী ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ‘যত মত তত পথ’ সর্বধর্ম মিলনের যে পথ দেখায়, নজরুলের এই ধারার সংগীতে সেই চেতনারই মহামিলনের মধুর সুর বেজেছে। যার ফলে নজরুলও সময়ের প্রয়োজনে ভক্তিগীতিতে মুসলিম-অমুসলিমের নিরাকার-সাকার বিভেদ, হিন্দু ধর্মের আন্ত-বিভাজনকে তোয়াক্কা করেননি। যেজন্যে নজরুল শ্যামা মায়ের কোলে বসিয়ে দিয়েছেন শ্যামকে । শ্যামা সংগীতে, ভক্ত ডাকছে শ্যামা মাকে, সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে বৈষ্ণবদের উপাস্য শ্যাম। যেমন :
১.
শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে জপি আমি শ্যামের নাম
মা হলো মোর মন্ত্রদাতা
ঠাকুর রাধাশ্যাম।।
ডুবে প্রেম-যমুনাতে
করবো খেলা শ্যামের সাথে... -(সংক্ষেপিত)
২.
শ্যামা বলে ডেকেছিলেম, শ্যাম হয়ে তুই কেন এলি?
ওমা লীলাময়ী মনের কথা কেমন করে শুনতে পেলি? -(সংক্ষেপিত )
৩.
ভালোবেসে আমার শ্যামা মাকে
যার যাহা সাধ সেই নামে সে ডাকে,
সেই নামে মা দেয় রে ধরা কেউ শ্যামা কয়, কেহ শ্যাম। -(সংক্ষেপিত)
জীবনবাদী সাধনার বলে নজরুল অদ্বৈতবাদী সমন্বয় মানসিকতা, একক স্রষ্টাকে সব সৃষ্টির মূলে অনুধাবন সক্ষমতা প্রকাশের শক্তি ও সাহস নজরুল আত্মস্থ করেছেন । তাঁর সার্বজনীন প্রেম চেতনার মূলে যে একক সত্তার প্রকাশ এবং সমন্বয় চেতনা আছে, তা তিনি ঐতিহাসিক সূত্রে ধারণ করেছেন। ভারতবর্ষে পীর-আওলিয়া, সুফি-দরবেশদের মাধ্যমে মধ্যযুগে যে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে এই ইসলাম স্থানীয় ধর্মীয় আচার বিশ্বাসের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে এক ধরনের সহজিয়া রূপ পেয়েছিল। পারস্য থেকে ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে আসা সুফিবাদী ইসলাম আর আরব দেশের প্রচলিত ইসলাম এই দুইয়ের মধ্যে আচরণগত এবং ভাবাদর্শগত পার্থক্য ছিল।
নজরুল পরিণত বয়সে নজরুল সুফি চেতনায় ঋদ্ধ, লালিত কবিদের সংস্পর্শে গেছেন। তাঁদের ‘অদ্বৈতবাদী’ চেতনার দ্বারা প্রাণিত হয়েছেন। তাঁদের রচনা চর্চায় অভিভূত হয়েছেন । মুগ্ধ ছিলেন ইরানি কবি হাফিজ, ওমর খৈয়াম, উর্দু কবি মীর (মৃত্যু : ১৮১০), মীর্জা গালিব (মৃত্যু : ১৮৭৯), এঁদের কবিতায়, গজলে, শের পাঠে, যাঁরা ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি। বলেছেনও নজরুল,
আমি বেশি পড়েছি গালিবকে, তাকেই বেশি জানি এবং তার কাব্য ভালবাসি। কিন্তু মীরের কবিতা আমাকে
পাগল করে দেয়। পাগল তো আল্লাহর ফজলে আমি আছিই। মীর আমার পাগলামিকে আরো প্রগাঢ় করে
তোলে। আমার এক পুরনো পীর (কবি হাফিজ) আছেন, যাঁর শরাবখানার দরজা আমার জন্য খোলা
সবসময় থাকে। (কানিজ ই বাতুল : ১৯৯৯ : উর্দু ভাষায় নজরুল চর্চা, নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, জন্মশতবর্ষ সংখ্যা,
বাংলা একাডেমি, ঢাকা: ২৩৩)
সংগীতের ভুবনে কাজী নজরুলের ইসলামের অনুরাগ মানবতাবাদী সার্বজনীন প্রেমে সিক্ত। সাম্যচেতনার আবহে লালিত এই প্রেম।
যার পরিচয় আছে ইসলাম ধর্মের গ্রন্থ কোরানে এরং রসুল’র (দ) হাদিসে। ইসলামী ভাবাদর্শে লালিত নজরুলের সাম্যচতনার বাণী,
১.
হিন্দু আর মুসলিম মোরা দুই সহোদর ভাই।
এক বৃন্তে দুটি কুসুম একভারতে ঠাঁই।।...
চাঁদ সুরুযের আলো হে কম-বেশি কি পাই
বাইরে শুধু রঙের তফাৎ ভিতরে ভেদ নাই।। (সংক্ষেপিত)
একই প্রার্থনার ভাষা ও ভাবসত্য নিম্নোক্ত দুটি সংগীতেও আছে, যার প্রথমটি ভক্তিমূলক, দ্বিতীয়টি ইসলামি সংগীত,
১.
দাও শৌর্য, দাও ধৈর্য, হে উদার নাথ,
দাও প্রাণ
দাও অমৃত মৃত জনে,
দাও ভীত-চিত জনে, শক্তি অপরিমাণ।
হে সর্বশক্তিমান।। ...
দাও পুণ্য প্রেম ভক্তি, মঙ্গল কল্যাণ।
ভীতি নিষেধের ঊর্ধে স্থির,
রহি যেন চির- উন্নত শির
যাহা চাই যেন জয় করে পাই, গ্রহণ না করি দান।
হে সর্বশক্তিমান।।’ (সংক্ষেপিত)
২.
খোদা এই গরীবের শোন শোন মোনাজাত।
দিও তৃষ্ণা পেলে ঠাণ্ডা পানি ক্ষুধা পেলে লবন-ভাত।।
মাঠে সোনার ফসল দিও
দিও গৃহ ভরা বন্ধু প্রিয়, দিও
হৃদয় ভরা শান্তি দিও- (খোদা) সেই তো আমার আবহায়াত।। (সংক্ষেপিত)
সুফিবাদী প্রেমিক, সাধক, বিশ্বাস করে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে মত-পার্থক্য বিভেদের জন্ম দেয় না। বিভেদের জন্ম দেয় অপ্রেমিক সত্তা। যাঁরা প্রেমিক তাঁরা মূলে একই স্রষ্টার বন্দনা করে । প্রেমিকের হৃদয় জলে ভেজা নরম কাদামাটির মতো, এই হৃদয় অন্য প্রেমিকের হৃদয়ে সহজে মিলে যায়, তা তিনি যে-ধর্মেরই হোন না কেন। নজরুল মানব ধর্মের মহামিলনের মোহনায় দাঁড়িয়ে প্রেমভাবে একই নিত্য ভগবানের বন্দনা করেছেন।
যুগের সন্ধিক্ষণে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব প্রকৃতই ছিল সময়োচিত। যাঁর সৃষ্টির সামগ্রিক চেতনার মূলে মানবতাবাদী প্রেম। মানুষকে তিনি ধর্ম দিয়ে পৃথক করেননি যখন রাষ্ট্র ও সমাজে বিভেদের ষড়যন্ত্র হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অবিশ্বাসের জন্ম দিয়ে ক্রমে ক্রমে আলাদা করে ফেলেছে। প্রেমিক বলেই তিনি হয়েছেন অদ্বৈতবাদী, সমন্বয়ী এবং অসাম্প্রদায়িক। মহামিলনের সুর নজরুলের গজল, ইসলামি গান, শ্যাম, শ্যামা সংগীতে বেজেছে। সমকালে রচিত তাঁর আধুনিক গানও জাগতিক প্রেমের উর্ধে ভিন্ন কিছুর ইংগিত দেয়। ফলে শতবর্ষ পেরিয়ে এসেও নজরুলের সংগীত ভাবনা আধুনিক, সমসাময়িক কালেও প্রাসঙ্গিক। এমন কি অনাগত কালেও। বর্তমান সমাজ তথা বিশ্ব থেকে দুর্বৃত্তায়নের মূল সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত না হওয়া পর্যন্ত নজরুলের কাব্য ও সংগীত সর্বকালে প্রাসঙ্গিক থেকে যাবে। নজরুল রাষ্ট্র ও সমাজে কখনো দুর্বৃত্তায়ন চাননি। আমরাও চাইনা। প্রত্যাশা করি, ‘মানুষ’ কবিতার সমন্বয় চেতনা মানব সমাজে উদ্ভাসিত হোক। মহামানবের মহামিলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে নজরুলের ১২৬তম জন্মজয়ন্তীতে ঘোষণা হোক,
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন,
মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
এই রণ-ভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা (কৃষ্ণ)
এই মাঠে হল মেষের রাখাল নবীরা খোদার মিতা। (মোহাম্মদ)৬
এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি (বেদ)
ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি। (বুদ্ধ)
এই কন্দরে আরব দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
এইখানে বসি’ গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান।
মিথ্যা শুনিনি ভাই
এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোন মন্দির-কাবা নাই। (সাম্যবাদী/ সাম্যবাদী)
