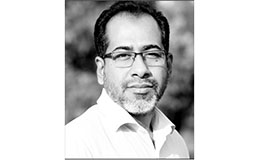
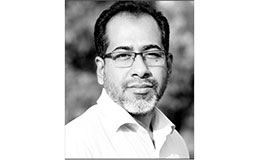
বেসরকারি
গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট
(র্যাপিড) আয়োজিত এক সাম্প্রতিক আলোচনায় তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন
বিজিএমইএ-এর সাবেক সভাপতি রুবানা হক স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা—অর্থাৎ
এলডিসি-থেকে বাংলাদেশের বেরিয়ে আসা প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি
বলেন, ২০২৬ সালের নভেম্বরে এলডিসি তালিকা থেকে চূড়ান্তভাবে বের হওয়ার কথা
থাকলেও, দেশের বাস্তবতা ও নিজস্ব সক্ষমতার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখতে
না পারলে ভবিষ্যতে তা বড় সংকটের সৃষ্টি করতে পারে। বক্তব্যে রুবানা হক যে
এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের বিপক্ষে সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং সেটি
বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের প্রায় সবার অভিমত বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।
আসল
সংকট তৈরি হয়েছে তখনই, যখন বিগত সরকার রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের জন্য
তথ্য-উপাত্ত নিজের ইচ্ছেমতো সাজিয়ে উপস্থাপন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, জনসংখ্যা
কম দেখিয়ে এবং জিডিপি বাড়িয়ে দেখানোর মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে মাথাপিছু জিডিপি
বাড়ানো হয়েছে। একইভাবে, মাথাপিছু আয়ও বাস্তব চিত্রের তুলনায় বেশি দেখানো
সম্ভব হয়েছে। ফলাফল, কাগজে-কলমে আমরা উন্নতির শিখরে আর মাঠে-ময়দানে মানুষ
অদৃশ্য উন্নয়নের নিচে চাপা পড়ে থাকে। এমনকি শ্বেতপত্র কমিটিও আর চুপ থাকতে
পারেনি-তারা স্পষ্ট বলেছে, এই উন্নয়নের গল্পে অতিরঞ্জনই আসল নায়ক।
জনসংখ্যা
আর জিডিপি-এই দুই মূল স্তম্ভকেই যেন বিগত সরকার ইচ্ছেমতো প্লাস্টার করে
উন্নয়নের বিল্ডিং বানিয়েছে। বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে কাগজে-কলমে এমন এক
চিত্র আঁকা হয়েছে, যেখানে আমরা প্রায় ইউরোপীয় সুখে আছি। শুধু তাই নয়,
অন্যান্য তথ্য-উপাত্তেও রীতিমতো রংতুলির কাজ হয়েছে, যাতে করে জাতিসংঘের
চোখে আমরা এলডিসি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যোগ্য হয়ে উঠি। ফলাফল? ২০১৮ ও ২০২১
সালে পরপর দুইবার জাতিসংঘের মূল্যায়নে উত্তীর্ণ হয়েছি-যেন উন্নয়নের কোনো
অলিম্পিক চলছে! যদিও ২০২৪ সালে আমাদের চূড়ান্ত উত্তরণের কথা ছিল, করোনা
মহামারির ছুঁতোয় সেই সময়টা দুই বছর পিছিয়ে ২০২৬ করা হয়েছে-যেন প্রকৃত
বাস্তবতা একটু সময় নিয়ে গুছিয়ে উঠবে।
বিগত সরকার এলডিসি উত্তরণকে যেন
নিজেদের অর্থনৈতিক কারিশমা হিসেবে সাজিয়ে প্রচার করেছে-এ যেন উন্নয়নের একটা
ঝকঝকে পোস্টার, যেটা বাস্তবের দেয়ালে একেবারে মেলে না। এতে তাদের ‘উন্নয়ন
বয়ান’টা আরও বিশ্বাসযোগ্য ঠেকেছে জনসাধারণের চোখে। কিন্তু পোস্টারের পেছনের
দেয়ালে যেসব ফাটল-যেমন রডের বদলে বাঁশ ব্যবহার, বা চারপাশে পানি রেখে
মাঝখানে কালভার্ট নির্মাণের মতো দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা-সেগুলো চেপে রেখে
উন্নয়নের নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে। নিজস্ব সক্ষমতা গড়ে তোলার আগে এভাবে
গ্র্যাজুয়েশনের পথ ধরা, মানে বন্যার সময় বাঁশের সাঁকোতে হাইওয়ে চালু করা।
এই
কারণেই রুবানা হকের মতো শিল্প মালিকরাও এলডিসি থেকে উত্তরণের বিষয়ে
সতর্কতা ব্যক্ত করছেন। তারা ভালোভাবেই জানেন, গ্র্যাজুয়েশনের পর বাংলাদেশের
সামনে কত বড় সংকট ও চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। তবু, বর্তমান অন্তর্বর্তী
সরকার বিগত সরকারের দেওয়া তথ্য-উপাত্তকে ভিত্তি করে গ্র্যাজুয়েশনের পক্ষে
সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, এখন এই গ্র্যাজুয়েশনের
নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের হাতের বাইরে চলে গেছে।
যেহেতু আমরা পরপর দু’বার
জাতিসংঘের মূল্যায়নে উত্তীর্ণ হয়েছি, তাই পিছিয়ে যাওয়ার পথ সহজে সম্ভব
নয়-তথাপি কিছু মানুষ পেছনে ফিরে যাওয়াকে আফগানিস্তানের মতো দেশের সঙ্গে
তুলনা করে থাকেন। এই ধরনের তুলনার সমালোচনা করে রুবানা হকসহ অন্যরা দেশের
বাস্তবতা বুঝে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।
অবশ্য
অন্তর্বর্তী সরকার চাইলে জাতিসংঘকে দেশের মন্দ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা
জানাতে পারত, এমনকি ভুয়া তথ্য-উপাত্তের বিষয়টাও সরকারি ব্রিফিংয়ে তুলে ধরতে
পারত। কিন্তু র্যাপিডের ওই অনুষ্ঠানেই বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান
বললেন, সময় বাড়ানোর জন্য আবেদন তাদের কাছে ‘গ্রহণযোগ্য’ নয়-মাঝে মাঝে মনে
হয়, বাস্তবতার চেয়েও মনের ইচ্ছের ওপর তারা বেশি বিশ্বাস করেন। অর্থনৈতিক
সংকটে দেশের অবস্থা বুঝিয়ে বলে সময় চাইতে নারাজ সরকারের এই পদস্থ কর্মকর্তা
যেন বলছেন, ‘আমরা তো ঠিকই আছি, আর কথা বাড়াবেন না।’
গ্র্যাজুয়েশন করলে
বাংলাদেশের লাভ কী? এক কথায়, আমরা বিশ্ব পরিমণ্ডলে ‘গরিব দেশের’ তকমা থেকে
মুক্তি পাব এবং এর সঙ্গে নকল সুনাম বাড়বে। ফলে কী হবে? কিছু বৈশ্বিক
সংস্থার নজরে আসব, যা আমাদের ক্রেডিট রেটিং বা ঋণগ্রহণের মান উন্নত করবে।
ফলে উচ্চ সুদে বাণিজ্যিক ঋণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়ার সম্ভাবনা থাকবে।
কিন্তু সেগুলো ছাড়া আমাদের হাতে আসবে কি আসল কোনো সুবিধা? প্রশ্ন থেকে যায়,
এসবই কি বাংলাদেশে প্রকৃত উন্নয়নের পথপ্রদর্শক?
একটা গল্প মনে
পড়ে-গ্রামের এক দরিদ্র লোক যখন হঠাৎ করে অনেক টাকা-পয়সার মালিক হলেন, তখন
এলাকার ক্ষমতাধর মাতব্বরা তাকে নিজেদের সালিশ-দরবারে পাশের চেয়ারে বসার
জন্য ডেকে নিতে শুরু করলেন। পাশের বেঞ্চে বসতে পারার সুখে আহ্লাদে আটখানা
লোকটির মতো হবে আমাদের অবস্থা। হয়তো আমরা এখন বড় বড় দেশের সঙ্গে পাশের
বেঞ্চে বসার সুযোগ পেতে যাচ্ছি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেই সুযোগ পেয়ে আমরা
কতটা সত্যিই ক্ষমতা বা সম্মান অর্জন করতে পারব? দেশের বাস্তবতা কিন্তু
অনেকটাই আলাদা-সেখানে পাশের চেয়ারে বসলেও আসল কাজ এবং সিদ্ধান্ত আমাদের
হাতে থাকে না।
বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে বলে আমরা আশা করছি, সেখানে সবচেয়ে
বড় বাধাগুলো কী? দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, পণ্য বিদেশে পাঠাতে সময়
বেশি লাগা তথা বন্দরের লিড টাইম বেশি। এই সমস্যাগুলো কি আগামী বছর বা তিন
বছরে সমাধান হবে? চট্টগ্রাম বন্দরের নিউ মুরিং টার্মিনাল বিদেশি অপারেটরদের
হাতে দেওয়া যায়নি, দেওয়া যথাযথ হবে কিনা এ নিয়ে বিস্তর আলাপ রয়েছে।
গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান কবে হবে, তাও জানা নেই। উচ্চ মূল্যের এলএনজিতে
শিল্পখাত নির্ভরশীল। এসব সমস্যা সমাধান না হলে গ্র্যাজুয়েশনের পর বিনিয়োগ
কতটুকু আসবে, তা বোঝা কঠিন নয়।
গ্র্যাজুয়েশনের সুবিধা শুধু সুনাম, উচ্চ
সুদে ঋণ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির আশায় সীমাবদ্ধ। কিন্তু যা হারাব, তার মোকাবেলার
সক্ষমতা আমরা এখনও তৈরি করতে পারিনি। অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার উদ্যোগ
রাজনৈতিক চাপে পুরোপুরি বাস্তবায়ন হবে না। দ্রুত নির্বাচনের দিকে এগোচ্ছে
সরকার। রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় এলে প্রতিষ্ঠানগুলো কতটুকু উন্নত হবে, তা
অজানা। কাক্সিক্ষত উন্নতি না হলে দুর্বল অবস্থায় গ্র্যাজুয়েশনের দৌড়ে
মাঝপথে ছিটকে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে।
এলডিসি দেশ হিসেবে আমরা বিশ্ব বাণিজ্যে
শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছি, যা হারাতে হবে। যদিও ইউরোপ ২০২৯ পর্যন্ত সময়
দেবে। কিন্তু ট্রাম্পের শুল্কনীতির কারণে পোশাক শিল্পে ৩৫ শতাংশ অতিরিক্ত
শুল্কের চাপে রপ্তানিকারকরা ধাক্কার মুখে। আগের ১৫ শতাংশ শুল্কের সঙ্গে
মিলে এটি ৫০ শতাংশ। এর ফলে গার্মেন্টস শ্রমিকদের কাজ হারানোর আতঙ্ক তৈরি
হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতারা এই শুল্কের চাপ মালিকদের ওপর দিলে শ্রমিক
ছাঁটাই হবে। জাপান, কোরিয়া, ব্রাজিলের মতো উদীয়মান বাজারেও চ্যালেঞ্জের
মুখে পড়ব। এর জন্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তি প্রয়োজন, যার অগ্রগতি অজানা।
বাণিজ্যের
চ্যালেঞ্জ ছাড়াও স্বল্পসুদে ও সহজ শর্তে ঋণ পাওয়া বন্ধ হবে, যা উন্নয়ন
বাজেটের বড় অংশ জোগায়। গ্র্যাজুয়েশনের পর উচ্চ সুদে বাণিজ্যিক ঋণ পাওয়া
যাবে, যা বাড়াবে উন্নয়ন খরচ।
আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব আইন কার্যকর হওয়ার
প্রভাবও পড়বে প্রাত্যাহিক জীবনে। আগের মতো চাইলেই আমরা ফ্রিতে কোনোকিছু
ডাউনলোড করতে পারব না। নিউমার্কেটে বিক্রি হওয়া বিদেশি নকল বইয়ের জন্য
সরকারকে জবাবদিহি করতে হতে পারে। এই যে ফ্রি সফটওয়্যার ব্যবহার করে লেখাটা
লিখছি, তখন এইসব সফটওয়্যারের জন্য আমাদের পয়সা দিতে হবে।
ওষুধ তৈরির
ফর্মুলা কিনে আনতে হবে। স্বল্পন্নোত দেশ হওয়ায় এতকাল এসব ফ্রিতে পেয়েছি
আমরা। এই তালিকা থেকে বের হলেই এসব সুযোগ হারাতে হবে। এক লাফে ওষুধের দাম
বেড়ে যাবে, তেমনি দৈনন্দিন তথ্য-প্রযুক্তির অনুষঙ্গগুলোর খরচও বাড়বে।
শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত বিশ্বে বৃত্তি কমে যাবে।
এই চ্যালেঞ্জ
মোকাবেলায় আমাদের প্রস্তুতি কতটুকু? জনগণের আয় কি এত বেড়েছে যে
গ্র্যাজুয়েশনের পর বাড়তি খরচ সামলানো যাবে? গত পাঁচ দশক এলডিসির সুবিধা
নিয়ে অর্থনীতিতে ভালো করেছি। এখন প্রস্তুতিহীন উন্নয়নশীল দেশে পা রেখে কী
তা হারাতে চাই?
ব্যবসায়ীরা এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের বিপক্ষে কথা বলছেন,
কারণ এতে তারা যে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হবেন তার জন্য নিজস্ব ব্যবসাতেও
সংস্কার আনতে হবে। সেটা করতে গিয়ে যদি নিজের লাভের অংক কমে আসে তাহলে তিনি
শ্রমিকের দিকে চাইবেন না। পরিস্থিতি খারাপ দেখলে বেশিরভাগ ব্যবসায়ী বিদেশে
পাড়ি জমাবেন।
বিপরীতে পরিবার নিয়ে অসহায় পরিস্থিতির মুখে পড়বে শ্রমিক
তথা দেশের স্বল্প আয়ের সাধারণ মানুষ। যেসব অর্থনীতিবিদ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ঘরে বসে এলডিসির পক্ষে কথা বলছেন, তারা টিসিবির লাইনে পণ্য কেনার জন্য
কস্মিনকালেও দাঁড়াননি। যেসব শ্রমিক বা নিম্নবিত্ত মানুষ দাঁড়ায় তারাই
একমাত্র জানে তাদের কষ্ট কতটুকু।
তাই সাধারণ জনগণের কথা ভেবে সরকারকে
সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা অবশ্যই এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন করব, কিন্তু
সেটা আগের সরকারের ভুয়া তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে নয়। বরং নিজস্ব
ভিত্তি মজবুত করেই আমরা এগিয়ে যাব। যাতে গ্র্যাজুয়েশন পরবর্তী
চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে গিয়ে আমাদের পেছন দিকে যাত্রা করতে না হয়।
লেখক: যুগ্ম বার্তা সম্পাদক (বিজনেস ডেস্ক), সময় টেলিভিশন।
