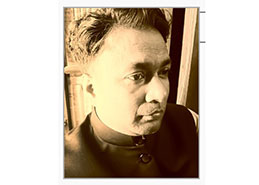

জীবনানন্দ
দাশ বরিশালের সন্তান। বরিশাল শহরে তাঁর জন্ম। বরিশাল শহরেই তাঁর বাল্য
কৈশোর ও প্রথম-যৌবন অতিবাহিত হয়েছে। পূর্বপুরুষের আদিনিবাস ছিল ঢাকা
বিক্রমপুরে। পিতামহ সর্বানন্দ কর্মব্যপদেশে বিক্রমপুর ছেড়ে এসে বসতি স্থাপন
করেন বরিশাালে। পরে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। এই বৈদ্য-পরিবারের কৌলিক
উপাধি ছিল দাশগুপ্ত। জাতিভেদহীন ব্রাহ্মসমাজে এসে সর্বানন্দ হলেন
দাশগুপ্তের বদলে শুধুমাত্র দাশ। সেই থেকে বরিশালের সর্বানন্দভবনের এই
বিশিষ্ট পরিবারটি ‘দাশ পরিবার’ নামে বিখ্যাত হল। সর্বানন্দের দ্বিতীয়
সন্তান সত্যানন্দ। তাঁরই প্রথম পুত্র কবি জীবনানন্দ। জীবনানন্দের
শিক্ষাব্রতী পিতা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মিক শিষ্য। মাতামহ ছিলেন
কবি। মাতা কুসুমকুমারীও। তাঁর “ছোটনদী দিনরাত বহে কুলকুল / পরপারে আমগাছে
থাকে বুলবুল-” / অথবা “আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে / কথায় না বড় হয়ে কাজে
বড় হবে; ” -প্রভৃতি মাতৃরচিত কবিতা ছিল শিশু জীবনানন্দের অস্ফুট কণ্ঠের
প্রথম কলকাকলি। কবির ছোট বোন সুচরিতা দাশ লিখছেন, ‘বাবা যদি দিয়ে থাকেন
তাঁকে সৌরতেজ-প্রাণবহ্নি, মা তাঁর জন্যে সঞ্চয় করে রেখেছেন স্নেহমমতার
বনচ্ছায়া, মৃত্তিকাময়ী সান্ত্বনা’।
কবিধাত্রী বরিশালের প্রকৃতিও
জীবনানন্দের কবিমানসকে বিস্ময়রাগে রঞ্জিত করেছে। ‘আকাশে অনাদি অনন্ত
ইন্দ্রনীল আর ধরণীর দিগন্ত ছুঁয়ে আস্তীর্ণ শ্যামলতা নয়ন-মন মগ্ন করে
রেখেছে, চেতনায় জ্বালিয়ে দিয়েছে সলজ্জ-শিখা ভালো-লাগার ভালোবাসার আনন্দে
থরথর করে কাঁপো-এমনি মোহমেহদূরতা সে দীপের আলোয়। অস্ফূট শৈশব থেকে প্রাণময়
কৈশোর ও যৌবনের দীর্ঘদিন কেটেছে বরিশালে-এমনি করে।’ [সুচরিতা দাশ]
সর্বনন্দভবনের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে একটি কিংবদন্তি আছে। রূপকথার মতোই তা
রোমাঞ্চকর। সুচরিতা লিখছেন, ‘সেই এক গল্প ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষের
সম্পর্কে, যাঁরা অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের একজনকে নাকি
পরীতে পেয়েছিল। জ্যোৎস্নারাতে ধানক্ষেতের উপর দিয়ে তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে যেত
পরীরা, ভোরের আলোয় তাঁকে পাওয়া যেত শিশিরঝলমল সোনার ধানক্ষেতের পাশে। তাঁর
বিছানায় ছড়ানো থাকতো কাঁচা লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি। তারপর বহুযুগ পার হয়ে
গেছে। এঁদেরই উত্তরপুরুষ জীবনানন্দ।’
এই আশ্চর্য কিংবদন্তিটি
জীবনানন্দের কবিমানস সম্পর্কে একটি নিগূঢ় সংকেত বহন করছে। জীবনানন্দও পরীতে
পাওয়া কবি। সৌন্দর্যতনু প্রেমের পরীরা তাঁকে জ্যোৎস্নারাতে ধানক্ষেতের উপর
দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেত এক অতীন্দ্রিয় রহস্যলোকে। অবোধপূর্ব সেই রহস্যজগতের
উপলব্ধির কথাই তিনি বলেছেন তাঁর মরমিয়া আলো-আঁধারি ভাষায়।
জীবনানন্দ
ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র, ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। ১৮৯৯ সালের ১৮
ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্ম। আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত বরিশাল স্কুলে আর কলেজে
মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত পড়ে কলকাতায় যান প্রেসিডেন্সি কলেজে সাম্মানিক
ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হয়ে। ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাশ করে কলকাতায় সিটি
কলেজে কর্মজীবন শুরু করেন। কিছুদিন পরে কলেজ থেকে তাঁর চাকরি যায়। তারপর
কিছুদিন দিল্লিতে এক কলেজে কাজ করে জীবনানন্দ আবার ফিরে আসেন বরিশালে।
ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপক হয়ে দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত এখানে ছিলেন।
দেশবিভাগের পরে তিনি চলে যান কলকাতায়। জীবনের বাকি দিনগুলি মুখ্যত
কলকাতাতেই অতিবাহিত হয়। ১৯৫৪ সালে দৈবদুর্ঘটনায় মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে
যখন তাঁর মৃত্যু ঘটে, তখন তিনি ছিলেন হাওড়া গালর্স কলেজের অধ্যাপক।
‘প্রকৃতিকে
নিবিড়ভাবে অনুভব করেন না এমন কোনো কবি নেই; কিন্তু সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির
ভিতর দিয়েই গ্রহণ ও প্রকাশ করেন এমন কবির সংখ্যা অল্প। তাঁরাই বিশেষভাবে
প্রকৃতির কবি। আমার মনে হয়, আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে একজনকে এই বিশেষ
অর্থে প্রকৃতির কবি বলা যায়, তিনি জীবনানন্দ দাশ।’ [কালের পুতুল, প্রথম
সংস্করণ, বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দের ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’র আলোচনা-প্রসঙ্গেই এই
মন্তব্য করেছিলেন। বরিশালের জীবনানন্দ সম্পর্কে এই মন্তব্য অক্ষরে-অক্ষরে
সত্য। কিন্তু কলকাতার জীবনানন্দ সম্পর্কে সর্বাংশে সত্য নয়। আসলে মহানগরীর
জীবন ও মনন জীবনানন্দের কবিকল্পনাকে নবরূপ দান করেছিল। তাই তাঁর
কাব্যসাধনাকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক, বরিশালের
প্রকৃতি-প্রভাবিত প্রথম যুগ; দুই, কলকাতার নাগরিকতা-প্রভাবিত দ্বিতীয় যুগ।
প্রথম যুগের কাব্যগ্রন্থ হল ‘ঝরা পালক’ (প্রকাশ ১৩৩৪। ১৯২৭), ‘ধূসর
পাণ্ডুলিপি’ (প্রকাশ ১৩৪৩। ১৯৩৬), ‘রুপসী বাংলা’ (রচনাকাল ১৩৪৩-৪৪), ‘বনলতা
সেন’ (রচনাকাল ১৩৩২-১৩৪৬), এবং ‘মহাপৃথিবী’ (রচনাকাল ১৩৩৬-৪৮)। দ্বিতীয়
যুগের ফসল সংকলিত হয়েছে ‘সাতটি তারার তিমির’ (রচনাকাল-১৩৩৫-৫০), এবং ‘বেলা
অবেলা কালবেলা’ (রচনাকাল ১৯৩৪-১৯৫০) ও পরবর্তী রচনাবলীতে। কলকাতাপ্রবাস
জীবনানন্দের প্রকৃতিনিষ্ঠ কাব্যসাধনা থেকে তাঁকে সরিয়ে এনেছে। সমকালীন
যুগজীবনের স্খলন-পতন-ত্রুটি সম্পর্কে তিনি অধিকতর সচেতন হয়েছেন। কাব্যকে
তিনি বলেছেন, ‘কবিমনের সততাপ্রসূত অভিজ্ঞতা ও কল্পনাপ্রতিভার সন্তান।’
নাগরিক জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে তা৭র কবিভাষারও পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর প্রথম
যুগের কবিভাষা ছিল হৃদয়বেগপ্রধান, দ্বিতীয় যুগের কবিভাষা মননবেগপ্রধান।
প্রথম যুগের কবিভাষায় ছিল বিষণ্নচিত্তের বিস্ময়বেগ, দ্বিতীয় যুগের কবিভাষায়
দেখা দিয়েছে বিক্ষুব্ধ চিত্তের শ্লেষবক্রোক্তি।
জীবনানন্দের কাব্য ও
কবিমানসের বিশ্লেষণে বুদ্ধদেব বসু উক্তিটিকে পুনর্বিচার করে দেখা প্রয়োজন।
বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, জীবনানন্দ সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়ে গ্রহণ ও
প্রকাশ করেছেন। আধুনিক বাংলা কাব্যে এই বিশেষ অর্থে জীবনানন্দই একমাত্র
প্রকৃতির কবি। আমরা বলেছি, জীবনানন্দের প্রথম ভাগের কবিতা সম্পর্কে উক্তিটি
অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। কিন্তু বুদ্ধদেবের উক্তি এবং আমাদের স্বীকৃতির ফলে
জীবনানন্দের কবিমানস ও কবিধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সষ্টি হওয়াই
স্বাভাবিক। জীবনানন্দ প্রকৃতির কবি, -এই অর্থে যে প্রকৃতিই তাঁর সমস্ত
উপলব্ধির রূপক।
আসলে কিন্তু জীবনানন্দ প্রেমের কবি। প্রেমের কবি না বলে
বরং প্রেমের মিস্টিক বললেই তাঁর কবিসত্তাকে সম্যক্ভাবে বুঝতে পারা যাবে।
তাঁর সমস্ত চেতনার মর্মমূলে রয়েছে এক হারানো প্রেমের স্বপ্ন ও স্মৃতি। কবির
এই প্রেমচেতনা কোনো ব্যক্তিপ্রেমের ‘বিশ্লেষধিয়ার্তি’র উৎসমূল থেকে
উৎসারিত হয়ে থাকতে পারে, অথবা তা কবিমানসের ‘জননান্তরসৌহৃদানি’র
সংস্কারমাত্রও হতে পারে। কবিমানসের এই বিপ্রলন্তু-প্রেমচেতনাই কবিকে
বিশ্বমুখী করেছে। সংস্কৃত কবি বলেছেন, মিলনের চেয়ে বিরহই বরং ভালো, কেননা,
মিলনে প্রিয়াই বিশ্বকে আড়াল করে একেশ্বরী হয়ে বিরাজমান থাকেন-কিন্তু বিরহে
ত্রিভুবন তন্ময় হয়ে যায়। ‘সঙ্গে সৈব তথৈকা, ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।’
জীবনানন্দের ত্রিভুবনও তাঁর প্রেমচেতনায় তন্ময়ীভূত হয়েছিল।
আমরা বলেছি,
জীবনানন্দ, পরীতে-পাওয়া কবি। কথাটা এই অর্থে সত্য যে, জীবনানন্দের
প্রেমচেতনা এক অতীন্দ্রিয় ভাবাদেশে উদ্ভাসিত হয়েছে। তাঁর এই ভাবাদেশ
বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। ‘যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ’,-নয়নমনের সেই
অনধিগম্য লোকে রয়েছে তাঁর চিরপলাতকা মানসসুন্দরী। ভাষার অতীত তীর থেকে কবি
তাঁর মরমী চেতনাকে ভাষার তীরে পৌঁছে দেবার ক্লান্তিহীন চেষ্টা করেছেন
সারাজীবন। এই দুঃসাধ্য চেষ্টায় তিনি যতটা সফল হয়েছেন ততটাই কবি হিসেবে তাঁর
সফলতা। তাঁর কবিজীবনের এই অনন্যপরতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখলেই তাঁর
ব্যর্থতা ও সার্থকতার যথার্থ বিচার সম্ভব হবে।
‘ঝরা পালক’ জীবনানন্দের
কাব্যসাধনার ইতিহাসে প্রস্তুতি-পর্ব। কবি স্বমহিমায় প্রকাশিত হলেন তাঁর
দ্বিতীয় কাব্যসংকলন ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে। এই অদ্ভুত নামকরণের যথার্থ
তাৎপর্য আবিষ্কার করা কঠিন। কবির প্রসিদ্ধতম কবিতা ‘বনলতা সেন’-এর স্তবকে
তার একটি ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যেতে পারে-
“সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;”
শেষের
বাক্যটির অন্বয় এবং বাচ্যার্থ দুরূহ। আসলে ওই শেষ দুটি পংক্তি ‘বনলতা সেন’
কবিতার দুর্বল গ্রন্থি। কিন্তু ওর মধ্যেই যে বাচ্যাতিরিক্ত অর্থান্তরের
অভিব্যঞ্জনা আছে তাতেই ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ নামকরণের আভাস রয়েছে। পৃথিবীর সব
রং নিভে গেলে জোনাকির ঝিলমিল রঙে পাণ্ডুলিপির গল্প শুরু হয়। আমরা জানি
বরিশালের আশ্চর্য প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবনানন্দের মন গড়ে উঠেছে।
নিসর্গসৌন্দর্য তাঁর কাব্যে নতুন সৌন্দর্যও পেয়েছে। কিন্তু জীবনানন্দের
কাব্যলোক এক অস্পষ্ট-ধূসর স্বপ্নের মায়া দিয়ে গড়া। রূপময় বিশ্বের সব রং
নিভে যাবার পর তাঁর স্বপ্নমদির রসলোকের দ্বার অর্গলমুক্ত হয। শেষ পর্যন্ত
জীবনানন্দ প্রেমচেতনা প্রকৃতিচেতনা ও ইতিহাসচেতনার কবি। কিন্তু তাঁর
প্রকৃতিচেতনা ও ইতিহাসচেতনার মর্মমূলে রয়েছে তাঁর প্রেমচেতনা।
প্রকৃতি,
বিশেষ ভাবে বাংলার প্রকৃতি, অপরূপ রূপ পেয়েছে জীবনানন্দের ‘রূপসী বাংলা’
সনেটগুচ্ছ। ‘রূপসী বাংলা’ গ্রন্থাকার প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর পরে।
কবিতাগুলি ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ পর্যায়ের শেষদিকের ফসল। গ্রন্থে আছে সবশুদ্ধ
ষাটটি কবিতা; একটি অষ্টক ছাড়া বাকি সবগুলিই চতুর্দশপদী। ‘রূপসী বাংলা’র
সনেটগুলির অঙ্গসন্ধি শিথিল, বাণীবিন্যাস ভাস্কর্যধর্মী নয়, চিত্রধর্মী।
কিন্তু
কবিতাগুলি বাংলার পল্লীবধূর তুলসীমঞ্চে সাঁঝের প্রদীপের মতো স্নিগ্ধ,
কমনীয়, পবিত্র। বাঙালী কবি বাংলাদেশকে, দেশের প্রকৃতিকে, দেশের ঐতিহ্য ও
সংস্কৃতিকে প্রাণভরে ভালোবেসেছেন। প্রসাদগুণান্বিত সহজবোধ্য ভাষায়
জন্মভূমির প্রতি তাঁর জন্মজন্মান্তরের প্রেমের কথা বলেছেন। টীকাভাষ্যে কোনো
দূতীয়ালির প্রয়োজন নেই। পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে চিত্ত প্রসন্ন হয়ে উঠে:
(১) “তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও-আমি এই বাংলার পারে
রয়ে যাব,”
(২) “বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ,
খুঁজেিত যাই না আর:”
(৩) “আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে;
যেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজো আসে,
যেইখানে কল্কাপেড়ে শাড়ি প’রে কোনো এক সুন্দরীর শব
চন্দন চিতায় চড়ে-আমের শাখায় শুরু ভলে যায় কথা;
যেইখানে সবচেয়ে বেশি রূপ-সবচেয়ে গাঢ় বিষণ্নতা;
আসিয়াছে শান্ত অনুগত”
(৪) “বাংলার নীল সন্ধ্যা-কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে:
আমার চোখের ’পরে আমার মুখের ’পরে চুল তার ভাসে;
পৃথিবীর কোনো পথ এ-কন্যারে দেখেনিকো-দেখি নাই অত
অজস্র চুলের চুমা হিজলে কাঁঠালে জামে ঝরে অবিরত,
জানি নাই এত স্নিগ্ধ গন্ধ ঝরে রূপসীর চুলের বিন্যাসে
পৃথিবীর কোনো পথে:”
কবির
এই উদ্বেল হৃদয়াবেগ থেকেই এক ঝোঁকে এই কবিতাগুলির জন্ম হয়েছিল। পৃথিবীর
কোনো পথে রূপসীর চুলে বিন্যাসে এত স্নিগ্ধ গন্ধ ঝরে না, তাই বাংলার প্রতি
কবির এত গভীর ভালোবাসা! এ ভালোবাসা জন্ম-জন্মন্তরের। শুধু তাই নয়, বাংলার
প্রকৃতি বাঙালি জীবনের পরম আনন্দ ও পরম বেদনার সঙ্গে কীভাবে জড়িয়ে আছে,
প্রতীকের সাহায্যে কবি কখনো সেকথা বলেছেন। মনসামঙ্গলের বেহুলার জীবন
কবিমানসে সেই প্রতীকটি সৃষ্টি করেছে। কবি বলছেন:
“বেহুলাও একদিন গাঙড়ের জলে ভেলা নিয়ে-
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়-
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিলো, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিলো,-একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিলো ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিলো পায়।”
ছিন্ন
খঞ্জনার মতো ইন্দ্রের সভায় বেহুলার নাচ, আর তার পায়ের ঘুঙুরের মতো বাংলার
নদী মাঠ ভাঁটফুলের কান্না উৎকৃষ্ট কবিকল্পনার সৃষ্টি। বাংলার এই ভালোবাসা
যে পেয়েছে স্বর্গসুখ তার কাছে তুচ্ছ তো হবেই। কিন্তু তবু একদিন এই পরম
প্রেমকে চেড়ে মানুষকে চলে যেহে হবে। জীবনে মৃত্যুর ডাক কখন আসবে কেউ জানে
না:
“কখন মরণ আসে কে বা জানে-কালীদহে কখন যে ঝড়
কমলের নাল ভাঙে -ছিঁড়ে ফেলে গাংচিল শালিখের প্রাণ,
জানি নাকো;-তবু যেন মরি আমি এই মাঠ-ঘাটের ভিতর,
কৃষ্ণা যমুনার নয়-যেন এই গাঙুড়ের ঢেউয়ের আঘ্রাণ
লেগে থাকে চোকে মুখে-রূপসী বাংলা যেন বুকের উপর
জেগে থাকে; তারি নিচে শুয়ে থাকি যেন আমি অর্ধনারীশ্বর।”
শেষের
রূপকল্পটি অভূতপূর্ব। কৃষ্ণা যমুনার নয়, গাঙুড়ের ঢেউয়ের আঘ্রাণই কবি পেতে
চেয়েছেন। পরকীয়া আর স্বকীয়া প্রেমের প্রতীক হিসাবেই এই দুটি নদীর নাম
পাশাপাশি বসে এক নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। তারপরেই, বুকের ওপর রূপসী বাংলা
আর তার নিচে কবির মৃত্যুতীর্ণ সত্তার অধৃনারীশ্বর মূর্তিটির কল্পনা
অন্ধকারে বিদ্যুদ্বিকাশের মতো হঠাৎ-আলোর-ঝলকানিতে রসিকচিত্তকে বিস্ময়াবিষ্ট
করে তোলে।
মৃত্যুর পরে কী হবে সেকথাও কবিকল্পনায় রূপ পেয়েছে। একদিন
অন্ধকারে নক্ষত্রের নিচে যখন তিনি মৃত্যুর ঘুমে শুয়ে থাকবেন তখনও এই
ভালোবাসা বেঁচে থাকবে। নবজন্মের জাগ্রত চেতনায় দেখতে পাবেন তাঁর শ্মশানচিতা
মধুকুপী ঘাসে ভরে আছে। এই ভালোবাসা তাঁকে বারবার ডেকে আনবে বাংলার
ধানসিঁড়ি নদীটির তীরে:
“হয়তো মানুষ নয়-হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হ’য়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;”
কবি
বলছেন, যে-রূপ নিয়েই তিনি আসুন না কেন, যার রূপ তাঁকে জন্মে জন্মে
কাঁদিয়েছে সেই গোরোচনা গোরী, সেই শঙ্খমালা-চন্দ্রমালার খোঁজেই তিনি ফিরে
আসবেন বাংলার বুকে। কেননা তারা যে নানা রূপ নিয়ে বাংলার বুকেই বারবার
জন্মগ্রহণ করে-“
এ-বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
তাঁরে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো-বিশালাক্ষী দিয়েছিলো বর,
তাই সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।”
কবি
বলছেন, তাঁর সমস্ত কবিতা তাদের কথা মনে করেই লেখা। একদিন সেইসব সুন্দরীর
বেঁচে ছিল, আজ তারা নেই। কিন্তু তাঁর বিষণ্ন স্বপ্নে মৃত্যুর ঘুম ভেঙে তারা
আবার জীবনের বুকে ফিরে আসে-“
এ কবিতা লেখা
তাহাদের ম্লান চুল মনে ক’রে; তাহাদের কড়ির মতন
সে কত শতাব্দী আগে তাহাদের করুণ শঙ্খের মতো স্তন
তাদের হলুদ শাড়ি-ক্ষীর দেহ-তাহাদের অপরূপ মন
চ’লে গেছে পৃথিবীর সব চেয়ে শান্ত হিম সান্ত্বনার ঘরে;
আমার বিষণ্ন স্বপ্নে থেকে থেকে তাহাদের ঘুম ভেঙে পড়ে।”
‘রূপসী বাংলা’র কবি সেই অপরূপ সুন্দরীদের স্বপ্নেই মশগুল হয়ে আছেন। তাই তাঁর একমাত্র প্রার্থনা:
“আমার সোনার খাঁচা খুলে দাও, আমি যে বনের হীরামন:”
এই
সনেটগুচ্ছ জীবনানন্দ ‘বনের হীরামন’ হয়ে বাংলার নিসর্গ-প্রকৃতি, বাংলার
রূপকথা, আর প্রাচীন কবিকল্পনার উপাদান দিয়ে এক অপূর্ব-সুন্দর স্বপ্নলোক
রচনা করেছেন। সেই স্বপ্নলোকের স্রষ্টা জীবনানন্দকে চিনতে পাঠকের ভুল হবার
কথা নয়। কিন্তু ‘প্রথম বারে যেমন লেখা হয়েছিল ঠিক তেমনই পাণ্ডুলিপিবদ্ধ
অবস্থায় রক্ষিত’, ‘সম্পূর্ণ অপরিমার্জিত’ এই সনেটগুচ্ছে কলাকৃতির দৃঢ়পিনদ্ধ
রূপটি ফুটে ওঠে নি। কিন্তু যে আবেগে কবি বলছেন, ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি,
তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর’, সেই আবেগ বিসংবাদী হলেও বাংলার
প্রকৃতি আর লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি কবির আন্তরিক অনুরাগ রূপসী বাংলাকে
অপরূপ সৌন্দর্যে মন্ডিত করেছে।
‘বনলতা সেন’-এই জীবনানন্দ দাশ মাধ্যন্দিন
দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠলেন। বনের হীরামন নয়, অকূল সমুদ্রে সন্তরণক্লান্ত
প্রাণই তাঁর কবিচিত্তের সার্থক উপমান হয়ে উঠল: “আমি ক্লান্ত প্রাণ এক,
চারিদিক জীবনের সমুদ্র সফেন।”
তাছাড় ‘বনলতা সেন’-এ প্রমাণিত হল যে,
জীবনানন্দ ‘রূপসী বাংলা’র কবি হয়েও ‘মহাপৃথিবী’র কবি। তাই ‘বনলতা সেন’ আর
‘মহাপৃথিবী'তে-জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিকল্পনার তুঙ্গশিখরে আরোহণ করেছেন।
কোনো
একটি কবিতা দিয়ে জবিনানন্দ দাশের সমগ্র কবিসত্তাটিকে যদি চিনতে হয় তাহলে
সে কবিতার নাম ‘বনলতা সেন’। তিনটি স্তবক দিয়ে গড়া এই কবিতার মধ্যে কবির
স্বপ্নবৃত্তটি পূর্ণ হয়েছে। কবি বলছেন:
“হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদন্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।”
অতীতচারিতা
রোম্যান্টিক কবিমানসের ধর্ম। কিন্তু এখানে শুধু অতীতচারিতাই নয়, পৃথিবীর
পথে হাজার বছর ধরে ইতিহাস-পরিক্রমায় খন্ডদেশকাল পেরিয়ে কবি মহাকালের
মহাপৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। নিখিল ইতিহাসে কবির সেই মহাজীবনবোধের সঙ্গে
ওতপ্রোত হয়ে আছে একটি প্রেমের স্বপ্ন, একটি প্রেমের আকর্ষণ। সেই প্রেমেরই
স্বপ্নবিগ্রহ নাটোরের বনলতা সেন। জীবনের সফেন সমুদ্রে ক্লান্ত প্রাণের কাছে
বনলতা সেন বহন করে এনেছে দ্বীপের ভরসা-সবুজ ঘাসের দেশের আশ্রয়।
“চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য, অতিদূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে;”
বনলতা
সেনের পাখির নীড়ের মতো চোখে পরম আশ্রয়, পরম আশ্বাসভরা যে প্রেমের সাক্ষাৎ
কবি পেয়েছেন তার মধ্যেই রয়েছে কবিজীবনের পরম প্রাপ্তি। তারই স্বীকৃতি দিয়ে
কবিতাটি সমাপ্ত হয়েছে-
“সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
সব পাখি ঘরে আসে-সব নদী-ফুরায় এ-জীবনের সব লেন দেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।”
বনলতা
সেন কিন্তু কোন বিশেষ নারী নয়। সে নিখিল নারীসত্তার নামরূপমাত্র। কবি নানা
নামে সেই একই রহস্যময়ী নারীসত্তাকে বার বার ডেকেছেন। ‘চোখে যার শত
শতাব্দীর নীল অন্ধকার’ সেই শঙ্খমালা, ‘পৃথিবীর ভালো পরিচিত রোদের মতন যার
শরীর’ সেই সুদর্শনা, ‘পৃথিবীর বয়সিনী এক মেয়ের মতন যে’ সেই সুরঞ্জনা,
‘বিকেলের নক্ষত্রের কাছে যে এক দূরতর দ্বীপ’ সেই সুচেতনা, -নানা নাসে সেই
একই প্রেমময়ী নারীকে কবি সম্বোধন করেছেন।
জীবনানন্দের কবিভাষা ও
কাব্যশিল্প সম্পর্কে এবার ইঙ্গিতে দু-একটি কথা বলে এই আলোচনার উপসংহার রচনা
করব। আমরা বলেছি, রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কাব্যজগতে নতুন কবিভাষার
আবিষ্কর্তা হলেন জীবনানন্দ দাশ। তিনি আমাদের ভাষার প্রকাশক্ষমতা বাড়িয়ে
আমাদের সূক্ষ্ম সুকুমার অনুভূতিকে নতুন নতুন দিগন্তে প্রসারিত করেছেন।
ভাষাসৃষ্টির
ক্ষেত্রে জীবনানন্দের কবিদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যই প্রথমে লক্ষ করবার মতো। এই
বিশ্বভূবনকে-এই নিসর্গলোকের রূপ-রং-শব্দ-গন্ধকে তিনি নিজের ইন্দ্রিয় ও মন
দিয়ে নিজের মতো করে অনুভব করেছেন। তার ফলে আমাদের এই চিরপরিচিত জগৎ প্রথমে
কবির একান্ত নিজস্ব একটি মনোজগতে রূপান্তরিত হয়ে, তাঁর কলাকৃতিতে সম্পূর্ণ
নতুন রূপ নিয়ে, আমাদের কাছে ফিরে এসেছে। বাংলার সৌন্দর্যলংকৃত কবিভাষার
সৃষ্টিতে ভারতচন্দ্রের পরে মধূসূদনের কৃতিত্ব অসাধারণ। তারপর রবীন্দ্রনাথের
হাতে সে ভাষা রূপের জগৎ ও সুরের জগতে নব-নব বর্ণবৈভব ও ধ্বনিমাধুর্যে
ষড়ৈশ্বর্যময়ী হয়ে উঠেছে। জীবনানন্দের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব এই যে,
রবীন্দ্রনাথের বাণীবিশ্বের অধিবাসী হয়েও তিনি আরেকটি বাণীবিশ্ব রচনা করে
যেতে পেরেছেন।
ভাষার দিক দিয়ে জীবনানন্দ প্রাকৃত বাংলার প্রাকৃত ভাষার
কবি। ছন্দের দিক দিয়ে দীর্ঘ-বিলম্বিত মহাপয়ারই তাঁর কবিতার মুখ্য বাহন।
শব্দের সঙ্গে শব্দ যোজনা করে নতুন অর্থ ও অর্থান্তরের অগম পারে পৌঁছবার
অক্লান্ত প্রয়াসের ফলেই এই বিলম্বিত-পয়ার কবির নিত্য-সঙ্গী হয়েছে। অলংকারের
দিক দিয়ে জীবনানন্দ সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন উপমাকে। লুপ্তোপমা তাঁর
রহস্যময় ধূসর জগতে পৌঁছবার একটি প্রধান চাবি। অপূর্ব অদ্ভুত উপমান সৃষ্টিতে
তাঁর কলাকৃতি ক্লান্তিহীন ছিল। উপমায় উপমানের সাধারণ ধর্মকে সজ্ঞানে
লুকিয়ে রেখে তিনি ভাষার অর্থদ্যোতনাকে অনির্বচনীয়তার পথে অনুক্ষণ এগিয়ে
দিয়েছেন। কবির বনলতা সেনের চোখ পাখির নীড়ের মতো। কোন্ সাধারণ ধর্মে পাখির
নীড় চোখের উপমান হল সে-কথা কবি উহ্য রেখেছেন বলেই ভাষা অপরিসীম ব্যঞ্জনায়
ভাবময় সুরময় হয়ে উঠেছে।
ভাষাশিল্পে জীবনানন্দ রাসায়নিক শিল্পী।
হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন যেমনবিদ্যুৎস্পর্শে জলে রূপান্তরিত হয়, তেমনি কবি
শব্দের পর শব্দ বসিয়ে তাঁর অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞার বিদ্যুৎস্পর্শ
দিয়ে নব নব অর্থদ্যোতনা সৃষ্টি করেছেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক-“দেখেছি
মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল কুয়াশার;”
এখানে নরম, নদী, নারী,
ফুল, কুয়াশা-এই পাঁচটি শব্দ তাদের নিজস্ব অর্থসত্তা হারিয়ে, রাসায়নিক
মিশ্রণে একীভূত হয়ে, এমন একটি অর্থময়তা সৃষ্টি করেছে যা ব্যবহৃত শব্দের
একটিতেও নেই। শব্দের সঙ্গে শব্দের এই যৌগিক মিশ্রণ ঘটিয়ে জীবনানন্দ যে নতুন
কবিভাষায় জন্ম দিয়েছেন তা আমাদের উপলব্ধির জগৎকে চারুতায় ও সূক্ষ্মতায়
নতুন নতুন দিগন্তে সম্প্রসারিত করেছে।
