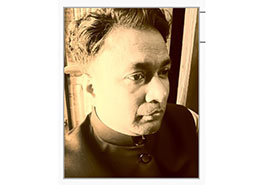
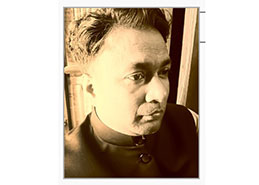
রবীন্ত্রনাথ
বলেছেন, ‘গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি/তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে
জানি।’ আমরা পড়ে আছি পৃথিবীর একটা কোণে, সেখান থেকে বিশ্বভুবনের ধারণা করব
কী করে? আমাদের অক্ষম কল্পনাশক্তি খুব বেশি দূরে আমাদের নিয়ে যেতে পারে না।
কবি-সাহিত্যিকদের কথা আলাদা। তাঁরা সুদূরের পিয়াসী, দূরাভিসারী তাঁদের মন।
কিন্তু তাঁরাও অবাধ ভ্রমণে অক্ষম। এমন যে রবীন্দ্রনাথ, তিনিও বলছেন, ‘মোর
ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই। কত গান, কত কবিতা, কত নাটক রচনা করলেন, তথাপি
বলেছেন, কথাগুলো পায়ে হেঁটে খুব বেশি দূর যেতে পারে না। কিন্তু যখনই গানের
কথায় সুর যোজনা করেছেন তখনই এই ভেবে তৃপ্তি বোধ করেছেন যে, গানের কথাগুলো
ডানা মেলে উড়তে শিখেছে। ভিন ভাষাভাষী যারা গানের কথা বুঝবে না, তারাও সুরের
ভাষা বুঝতে পারবে। কথা যদি মনকে না ছোঁয়, সুর মনকে ছুঁতে পারবে।, অন্যত্র
বলেছেন, ‘আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে।’ সংগীতজ্ঞ মহলে কথা এবং
সুর দুই-এর মধ্যে বহু কাল থেকে একটা দ্বন্দ্ব চলে আসছে। শাস্ত্রজ্ঞরা
বলেন, সুরই গানের ভাষা, কথার কোনো প্রয়োজনই নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজেও কথাকে
বলেছেন মুখরা। কিন্তু আমি বলি কী, মুখরাও মধুরা হতে জানে। রবীন্দ্রনাথ মূলত
কবি। কবিকে কথা দিয়েই কাব্য রচনা করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন সংগীত রচনা
করেছেন তখনও তিনি প্রথমে কবি, পরে সুরকার। যা হোক, সুরজ্ঞ ব্যক্তিরা যাই
বলুন, আমার কাছে রবীন্দ্রসংগীতের কথা মোটেই অনাবশ্যক নয়। কেননা, প্রতিটি
গানের কথাই কাব্যগুণে গুণান্বিত। সুরসংযোগে না শুনে যদি নিছক কাব্য হিসেবে
পাঠ করা যায়, তাহলেও তাঁর গানের মাধূর্য গোপন থাকে না। কাব্যগুণই তাঁকে
গীতময় করেছে। একশবার স্বীকার করব যে সুরের পাখা আছে ওড়ার ক্ষমতা আছে। তবু
বলব, গানের কথাও নিতান্ত পদাতিক নয়, কথারও পাখা আছে এর কথা আগইে বলেছি।
গীতবিতান সংগীত সংকলন গ্রন্থ হয়েও কাব্যগ্রন্থ। তিনি বলতে কি, আমি
গীতবিতানকেই বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বলে মনে করি।
বলে নেওয়া
ভালো, আমি সংগীতজ্ঞ মানুষ নই, রাগরাগিণীর জ্ঞান আমার নেই। রবীন্দ্রনাথ
যাদের পরিহাস করে বলেছেন “সুর-কালা” কিংবা বলেছেন “অ-সুর” আমি তাদের বলি।
কাজেই রবীন্দ্রসংগীতের সাংগীতিক রূপটার চাইতে কাব্যিক রূপটাই আমার কাছে বড়
হয়ে দেখা দিয়েছে। সুকণ্ঠ গায়ক-গায়িকার কণ্ঠে সে গান শুনে যে আনন্দ পেয়েছে
তাকে মনে করেছি উপরি পাওনা। সংগীতজ্ঞরা আমার সঙ্গে একমত হবেন না, সে কথা
জানি। একবার লখণৌ প্রবাসী একজন বাঙালি ওস্তাদের মুখে সংগীতের আলোচনা
শুনেছিলাম। তিনি শাস্ত্রীয় সংগীতে পণ্ডিত। চমৎকার বক্তা, মাঝে মাঝে গান করে
তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করছিলেন। মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। ভদ্রলোক কবি
আত্মপ্রসাদ সেনের প্রিয়পাত্র। এক সময়ে বললেন, আমি অতুলদাকে বলি, আপনি তো
গান লেখেন না, একেকটি কবিতা লেখেন। অর্থাৎ বলতে চেয়েছেন, সংগীত অত কথার
প্রত্যাশী নয়। দুটি-একটা পদই যথেষ্ট। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে রবীন্দ্রসংগীত
সম্পর্কেও উক্ত ভদ্রলোক ওই ধারণাই পোষণ করতেন। যাক্ সংগীতচর্চার কথা এবং
সুরের দ্বন্দ্ব কোনো কালেই শেষ হবে না। আমি গোড়াতেই স্বীকার করে নিচ্ছি যে
রাগরাগিণীতে অজ্ঞ বলেই আমার কাছে রবীন্দ্রসংগীত প্রধানত কথা-নির্ভর। বলা
নিষ্প্রয়োজন যে এটি সাংগীতিক আলোচনা নয; প্রবন্ধটি অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে
লেখা।
রবীন্দ্রসংগীতে গীতিকার এবং সুরকার দুই-ই রবীন্দ্রনাথ নিজে– কথা
তাঁর, সুরও তাঁর। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তিনি নিজেও কথার চাইতে সুরকে বেশি
প্রাধান্য দিচ্ছেন। গোড়ায় যে গানটির উল্লেখ করেছি তাতে বলেছেন, গানের ভিতর
দিয়ে যখন দেখেন (এখানে গান বলতে নিঃসন্দেহে সুর সংযোগে) তখন বিশ্বভুবনের
মূর্তিটা বদলে যায়, অনেক বেশি মনোহর হয়ে দেখা দেয়। বলছেন ‘তখন তারি আলোর
ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়।’ স্বীকার করতে বাধা নেই, ‘সুর তাঁর তারি আলোর
ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়।’ স্বীকার করতে বাধা নেই, সুর তাঁর যতখানি মনোহরণ
করে, আমাদেরও ততখানি করে বললে একটু বেশি বলা হবে। কেননা, ‘আলোর ভাষা’
আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়; ‘আকাশ ভরে ভালোবাসায়’ কথাটাও একটু ঝাপসা ঠেকে।
যদি বলতেন, মন ভরে যায় ভালোবাসায়, কথাটাও একটু ঝাপসা ঠেকে। যদি বলতেন, মন
ভরে যায় ভালোবাসায়, তাহলে কথাটা বোঝা আমাদের পক্ষে সহজ হতো। ‘আলোর ভাষা’
বলতে তিনি বুঝেছেন সুরের ভাষা। ওই সুরের ভাষা রবীন্দ্রনাথের কাছে যতখানি
সহজবোধ্য আমাদের কাছে ততখানি নয়। আসল কথা, সুরের প্রভাব রবীন্দ্রনাথকে যত
দূরে, যত গভীরে নিয়ে যেতে পারে আমাকে তা পারে না; কেননা, সুরের ভাষাটা আমার
জানা নেই। এ ছাড়া আরেকটা কথাও আছে; এ গানে আগাগোড়া যেসব কথা ব্যবহার করা
হয়েছে তা বেশিরভাগই অনুভূতিসাপেক্ষ। অনুভূতি ক্ষমতা সকলের সমান নয়। এর ফলে
গানের প্রত্যেকটি পদই আমাদের কাছে একটু ঝাপসা ঠেকে। লক্ষ করলে দেখা যাবে,
পরে যখন শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের জন্য গান রচনা করেছেন তার ভাষা অনেক
সহজ হয়ে এসেছে, কারণ সে ভাষা অনুভূতির ততখানি নয়, যতখানি উপভোগের। আনন্দের
আর সৌন্দর্যের উপকরণ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, যত পার দু’ হাত ভরে লুঠ করে নাও।
বলেছেন, ‘আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ নেব সে লুঠ করে।’
সংগীত রবীন্দ্রনাথের
সর্বক্ষণের সাথি। মনে একটা সুরের গুনগুনানি সারাক্ষণ লেগেই থাকত। বলেছেন,
গান আমি শিখিনি, গান আমি পেয়েছিলাম। এ তো আরও বড় কথা। অর্থাৎ কি না গান
আপনা থেকেই এসে তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিল। অশিক্ষিত পটুত্ব যাকে বলে সে খুব
উঁচু দরের জিনিস, তারই নাম প্রতিভা। তাহলেও বলব, জ্ঞাতসারে হোক, অজ্ঞাতসারে
হোক, সংগীতের সাধনা করেছেন আজীবন। রাগরাগিণী সম্পর্কে জ্ঞান ছিল সুগভীর।
সংগীতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই তা প্রকাশ পেত, এমনকি সাধারণ কথাবার্তারও।
‘ছিন্নপত্রের’ একটা চিঠিতে বলেছেন, ‘এতক্ষণ কোনো কাজ না থাকাতে নদীর দিকে
তাকিয়ে গুনগুন স্বরে ভৈরবী টোড়ি রামকেলি মিশিয়ে একটা প্রভাতী রাগিণী সৃজন
করে আপন মনে আলাপ করছিলাম, তাতে মনের ভিতর এমন একটা সুমধুর চাঞ্চল্য জেগে
উঠল, এমন একটা অনির্বচনীয় ভাবের আবেগ উপস্থিত হলো, মুহূর্তের মধ্যে আমার এই
বাস্তব জীবন এবং বাস্তব জগৎ আগাগোড়া তার মূর্তি পরিবর্তন করে দেখা
দিলে...।’
রাগরাগিণী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলে ভৈরবীর সঙ্গে টোড়ি এবং
রামকেলির মিশ্রণে যে সুর-মাধুরীর সৃষ্টি হয় তা বোঝার ক্ষমতা আমার নেই।
সেজন্য রবীন্দ্রসংগীতের মহিমা আমার কাছে প্রধানত কথা-নির্ভর। কথাই মনে
ভুলিয়েছে, সুর ব্যতিরকেও এর কাব্যগুণ গোপন থাকেনি। সুরের মাধুর্য থেকে
যেটুকু পেয়েছি সেটুকু অধিকন্তু। এ কথা নিশ্চিত যে, সুরের জ্ঞানটি
বিজ্ঞানসম্মত হলে উপভোগটি গভীরতর হতো। সুরের ভাষা যথাযথভাবে বুঝিনে বলে
কথার ভাষার ওপরেই আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে। গানকে পেতে হয় সুরে-রসে। সুরের
দিক থেকে যা বাদ পড়েছে, রসের দিক থেকে তা পুষিয়ে সেবার চেষ্টা করেছি। সুরের
মধ্যে রস যতখানি ধরা দেয়, কথার মধ্যে, বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীতে তার চাইতে
কিছু কম দেয় বলে মনে হয়নি। ইংরেজি বা অন্য ভাষায় অনূদিত ‘গীতাঞ্জলি’র রস
বিদেশিরা কথার মধ্যেই পেয়েছে, গীতের মধ্যে নয়।
বলে নেওয়া ভালো যে, আমার এ
আলোচনা কথা এবং সুরের দ্বন্দ্ব নিয়ে নয়। বিষয়টা ব্যাপকতর। রবীন্দ্রনাথ তো
শুধু গীতিকার বা সুরকার নন। কাব্যসাহিত্যের জগতে তিনি বলতে গেলে এক
বিশ্বকর্মা। গান, কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, মৌখিক ভাষণ, অগণিত
চিঠিপত্র, সব মিলিয়ে একটা গোটা জগৎ সৃষ্টি করে গিয়েছেন। নাম দেওয়া যেতে
পারে রবীন্দ্র-জগৎ। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, ‘বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু
জানি’ আমাদেরও তেমনি বলতে হয়, বিপুল রবীন্দ্র-জগতের কতটুকু আমরা জানি বা
বুঝি! যেমন তার বিস্তার তেমনি তার গভীরতা। কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস,
মন্দিরের ভাষণ এবং প্রবন্ধবলিকে যদি আলাদা আলাদা করে দেখি তাহলে বিরাট
রবীন্দ্র জগৎকে খণ্ডিতভাবে দেখা হবে, তার সমগ্র রূপটি পাওয়া যাবে না। গোড়ায়
উদ্বৃত গানটিতে রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, গানের ভিতর দিয়ে যখন বিশ্বভুবনকে
দেখেন তখনই তাকে ঠিকভাবে দেখেন এবং চেনেন, আমরাও তেমনি বলতে পারি,
রবীন্দ্রসংগীতের ভিতর দিয়ে যদি রবীন্দ্র-জগৎটিকে দেখি তবেই সে জগৎটিকে
সমগ্রভাবে দেখা যাবে, চেনা যাবে। কেননা ওই সংগীতের মধ্যে কাব্য তো রয়েছেই,
আছে যথেষ্ট নাটকীয়তা, তা ছাড়া ওই গানের মধ্যেই পাওয়া যাবে মন্দিরের ভাষণ
এবং প্রবন্ধবলির গভীর মননশীলতা। সৃজনশীল এবং মননশীল রবীন্দ্রনাথকে একাধারে
পেতে হলে আমাদের যেতে হবে গীতিবিতানের কূজন-মুখর উদ্যানে। সেখানে তিনি
নিজেকে যতখানি দিয়েছেন ততখানি আর কোথাও নয়। নিজেই বলেছেন, তোমাদের সুখের
দিনে, দুঃখের দিনে দিয়েছি রচি গান, ‘সে গানে মোর জড়ানো প্রীতি/সে গানে মোর
বহুক স্মৃতি/আর যা সব হোক্ অবসান।’ ‘তিনি নিজেই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ
আসন দিয়েছেন সংগীতকে।’
এত যে বিপুল পরিমাণে লিখেছেন, বলেছেন, তাতেও কি
গোটা মানুষটাকে আমরা চিনতে পেরেছি? তাঁর বহুমুখী প্রতিভা এবং বর্ণাঢ্য
ব্যক্তিত্ব যতখানি আমাদের চোখে ধরা দিয়েছে, ততখানি আমাদের মনশ্চক্ষে ধরা
দেয়নি। মানুষের মন বড় দুর্গম স্থান। মনের অন্তস্থলে মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছনো
বড় দুসাধ্য ব্যাপার। মনের গভীরতম কথা, গভীরতম চিন্তা ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই
থেকে যায়। শেকসপিয়র নিজের সম্পর্কে কোনো কথাই বলেননি। তাঁর জীবন সকলের কাছে
এক মহা রহস্য। ম্যাথু আর্নল্ড শেকসপিয়রকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আমরা তার
কূল পাই না। যতই ভাবি ততই অভিভূত হই। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অতখানি বলা চলে
না। তিনি কখনই আত্মগোপন করেননি। কী ভেবে কী করছেন সে কথা সর্বদাই খুলে
বলেছেন। কাজেই তিনি বোধের অগম্য নন, তবে খুব সহজবোধ্য নন, এ কথা স্বীকার
করতে হবে। দুর্বোধ্য এই কারণে যে রচনাবলির গহন অরণ্যে পাঠক একটু দিশেহারা
বোধ করে।
রবীন্দ্রনাথ কাজের মানুষ ছিলেন, কাজ ভালোবাসতেন। কিন্তু সে
কাজকে হতে হবে আনন্দময়। নিরানন্দ কাজ নিতান্তই বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। শুধু হুকুম
মেনে কাজ করলে চলবে না; কাজ করতে হবে মনের আনন্দে-কাজ করাকেই বলে
মনেপ্রাণে কাজ করা। গানের সুরেই বলেছেন, ‘আনন্দ সর্ব কালে, আনন্দ সর্ব
কাজে।’ চাষি মাঠে চাষ করছে, তাও বলছে, ‘আমরা চাষ করি আনন্দে।’ যে কাজই করুক
না কেন, তার মধ্যেই একটু আনন্দের আমেজ থাকবে। বলেছেন ‘মোদের যেমন খেলা
তেমনি যে কাজ।’ খেলায় আর কাজে তফাত রাখেননি। কাজটাও খেলার মতোই উপভোগ্য
হবে। মননশীল মানুষ ছিলেন বলেই মনটাকে সকল কাজে ডেকেছেন। জানতেন যে, যে-কাজে
মন নেই, সে-কাজে প্রাণ নেই।
রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে কোথাও একটা
ছেলেমানুষ বা চিরকিশোর লুকিয়ে ছিল। সে ছেলেমানুষটা যখন-তখন মাথাচাড়া দিয়ে
উঠত। বয়স তাকে কখনো দাবিয়ে রাখতে পারেনি। হঠাৎ বলে উঠলেন, ‘ওরে ওরে ওরে
আমার মন মেতেছে তারে আজ থামায় কে রে।’ থামাবার চেষ্টা তিনি নিজেও করেননি,
অপরকেও করতে দেননি। মেতে ওঠার একটা প্রবণতা বরাবর থেকে গিয়েছিল। ‘পাগলা
হাওয়ার বাদল দিনে পাগল আমার মন জেগে ওঠে।’ পাগলামি তো বটেই, মাতলামি করতেও
কোনো আপত্তি ছিল না। বলছেন ‘বৃষ্টি-নোশা-ভরা সন্ধ্যা বেলা কোন বলরামের আমি
চেলা।’ বলরাম একটু অতিমাত্রায় মদ্যাসক্ত ছিলেন। কবি বলছেন, আজকের এই বৃষ্টি
ভেজা সন্ধ্যাবেলায় আমাকে যেন নেশায় পেয়েছে। প্রকৃতির এই পাগলামির সঙ্গে
তাল মিলিয়ে আমারও বলরামের চেলা সেজে মাতলামি করতে ইচ্ছে করছে। ওই
ছেলেমানুষি এবং পাগলামি মিলে কবিকে করেছে চিরতরুণ আর তাঁর কাব্যকে করেছে
প্রাণবন্ত। মনকে কী করে চিরনবীন, চিরতরুণ রাখা যায়, এটি ছিল তাঁর চিরজীবনের
সাধনা। শুধু তাই নয়, এটি রবীন্দ্র-জীবন-দর্শনের একটা মূল কথা। বার্ধক্যকে
রোধ করা যায় না, কিন্তু তাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। দেহের ওপরে প্রাধান্য
বিস্তার করুক, কিন্তু মন যেন জরাগ্রস্ত না হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে সে
দুর্দৈব ঘটেনি। দেহ অশক্ত হয়েছিল কিন্তু মন শেষ পর্যন্ত ছিল সম্পূর্ণ সতেজ
এবং সজীব। জীবনের সর্বশেষ রচিত কবিতাটিতে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ রেখে
গিয়েছেন। সেখানেও কণ্ঠ পূর্ববৎ তরুণ।
মানুষটি একাধারে মননশীল এবং
সৃজনশীল। মননের মধ্যেই সৃজনের বীজ। ভাবুক মন সারাক্ষণই মনের মধ্যে নানা
ভাব, নানা চিন্তা নিয়ে খেলা করছে। সকল সৃষ্টির মূলে ওই মনের খেলা। মন না
খেললে সৃষ্টি হয় না। সৃজনশীল মন সর্বক্ষণ খেলার আনন্দে মত্ত। অকারণ পুলকে
কবির মন ক্ষণে ক্ষণেই গেয়ে ওঠে; তখনই কবিতার জন্ম হয়েছে, গান রচিত হয়েছে।
আনন্দ তৃষার সঙ্গে যুক্তি ছিল সৌন্দর্য-তৃষ্ণা। ওই সৌন্দর্য-বোধটি পৈতৃক
সম্পত্তি। মহর্ষি একদিকে যেমন ভগবদ-প্রেমিক, অপর দিকে তেমনি
সৌন্দর্য-প্রেমিক। তিনি বলতেন, শাস্ত্রে বিশ্ব-স্রষ্টাকে বলা হয়েছে
প্রজ্ঞান-ঘন। আমার যৎসামান্য জ্ঞান, তাই দিয়ে আমি জ্ঞান-স্বরূপের ধারণা করব
কী করে? সে জন্যে আমি তাঁর ধ্যান করি সৌন্দর্য-ঘন রূপে, সৃষ্টির অনন্ত
সৌন্দর্য আমার চোখের সম্মুখে প্রসারিত। এই অন্তহীন সৌন্দর্যের মধ্যেই আমি
প্রজ্ঞান-ঘনকে সৌন্দর্যঘন রূপে প্রত্যক্ষ করি, উপলব্ধি করি। রবীন্দ্রনাথেরও
মনপ্রাণ ওই সৌন্দর্যে মোহিত। এই যেমন বলেছিলেন, ‘তার অন্ত নাই গো যে
আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ’ তেমন আবার বলতে পারতেন, ‘তার অন্ত নাই গো যে
সৌন্দর্যে ভরা এই বিশ্ব ভূমণ্ডল’। উল্লেখ করা যেতে পারে যে পৃথিবীর
কবিকুলের মধ্যে নিকটতম আত্মীয়তা বোধ করেছেন কীট্স-এর সঙ্গে। নানা সময়ে,
নানা প্রসঙ্গে কীট্স-এর উক্তি, ঞৎঁঃয রং ইবধঁঃু বারংবার উল্লেখ করেছেন।
এটিকে তিনি একটা অতি প্রগাঢ় উক্তি বলে মনে করতেন। কীট্স-এর ন্যায়
রবীন্দ্রনাথও বলতে পারতেন ‘ঞৎঁঃয রং ইবধঁঃু, ইবধঁঃু রং ঞৎঁঃয’ আনন্দের
সাধনা এবং সুন্দরের আরাধনা এই দুই নিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবন। তিনি যে দেবতার
পূজা করেছেন তিনি একদিকে আনন্দরূপমমৃত যদ্বিভাতি, অপর দিকে ‘সুন্দর
হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন ফুলহার।’ জীবনকে দেখেছেন একটা উৎসব হিসেবে। প্রতিটি
দিন যেন একটা আনন্দের বার্তা নিয়ে দেখা দেয়। প্রতি দিনের সূর্যোদয়কে দুহাত
বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করেছেন। বলেছেন, ‘আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার।’
ইংরেজ কবি যখন বলেছেন, ‘ঞৎঁঃয রং ইবধঁঃু’ তখন তিনিও একই ভাব নিয়ে
সূর্যোদয়কে দেখেছেন। প্রতি দিনের সূর্যোদয়ে আলোর ঝরনায় না করেছেন
রবীন্দ্রনাথ। বলেছেন, ‘আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও।’ প্রাত্যহিকতার
অভ্যাস-জীর্ণ জীবনে মনের ওপরে যে মলিনতার প্রলেপ পড়ে যায় এই আলোর ঝরনায় তা
ধুয়ে নিতে হবে। আনন্দ এবং সৌন্দর্যের স্বাদ যে একবার পেয়েছে তার
মুক্তি-সøান হয়ে গিয়েছে। আনন্দ তার মনকে আজীবন সজীব রাখবে, সৌন্দর্যবোধ তার
স্বভাবকে মাধুর্যময় করে তুলবে। সুন্দর এবং আনন্দ দুটি অঙ্গাঙ্গিভাবে
যুক্ত, একে অন্যের মধ্যে লীন। যেখানে সুন্দরের সাক্ষাৎ মিলল সেখানেই আনন্দ
এসে জুটল। কবি দুটিকে আলাদা করে দেখেননি। যে মুহূর্তে বলেছেন, ‘জগতে
আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ’ যে মুহূর্তেই আবার বলেছেন, ‘নয়ন আমার রূপের
পুরে/সাধ মিটিয়ে বেড়ায় ঘুরে/শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন।’ যখন বলেছেন,
‘আনন্দধারা বহিছে ভুবনে’ তখন বলতে ভোলেননি, ‘দিন রজনী কত অমৃতরস উথলি যায়
অনন্ত গগনে/পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া।’ এই অমৃতরসই সৌন্দর্য-সুধা,
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা দিবানিশি তাই দান করছে।
জীবনের মধ্যে একটা
উল্লাসের ভাব আছে। রবীন্দ্রনাথ সে উল্লাসের ভাবটিকে শুধু ছেলেমেয়েদের মনে
নয়, সমস্ত আশ্রমবাসীর মনে ধরিয়ে দিয়েছেন। বৎসরব্যাপী নানা উৎসবের আয়োজন,
বারো মাসে তেরো পার্বণ। পার্বণহীন বাকি দিনগুলোও নিতান্ত নিথর নির্জীব ছিল
না। স্বভাবগুণে প্রতিটি দিনই ছিল প্রাণচঞ্চল, আনন্দমুখর।
নানা
দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটনের মধ্যেও জীবনটাকে সাধ্যমতো উপভোগ্য করার দিকে
সর্বক্ষণ নজর ছিল। অল্পের মধ্যে ক্ষীরটুকু গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।
রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন, ‘আমার মতে জীবনটাতে ভালোটারই প্রাধান্য/মন্দ
যদি তিন চল্লিশ ভালোর সংখ্যা সাতান্ন।’ এজন্য তাঁর অগণিত গানে ও কবিতায়
একটা যেন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের ভোজে আমন্ত্রণ। জীবনে উল্লাসের কথা আগে
বলেছি। আমাদের বর্ষার ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যেও সেই উল্লাসের ভাবটা আছে।
ছেলেমেয়েদের দেখেছি বৃষ্টিতে ভিজে প্রাণের আনন্দে গান করছে, ‘আজ বারি ঝরে
ঝর ঝর ভরা বাদরে।’ বলেছেন, ‘অন্তরে আজ কী কলরোল, দ্বারে ভাঙল আগল।’ বর্ষা
গিয়ে শরৎ এসেছে তো ছেলেমেয়েরা প্রাণ খুলে গেয়েদ্বে, ‘মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি, আজ আমাদের ছুটি।’ কাশের গুচ্ছ এবং শেফালি মালায় সজ্জিতা
শারদলক্ষ্মীকে উদ্দেশ করে গান ধরেছেন, ‘আমার নয়ন ভুলানো এলে/আমি কি হেরিলাম
হৃদয় মেলে।’ বসন্ত সমাগমে ছেলেমেয়েরা বৈতালিকে আশ্রম পরিক্রমা করে গেয়েছে,
‘আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।’ প্রকৃতির ভান্ডারে যে অফুরন্ত
সৌন্দর্য-সম্ভার, তার প্রতি নিরন্তর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।
আপাতদৃষ্টিতে
মনে হতে পারে, রূপে গুণে, ধনে মানে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে বিধাতাপুরুষ
রবীন্দ্রনাথকে একেবারে উজাড় করে দিয়েছেন। তা দিয়েছেন বটে, কিন্তু এক হাতে
যেমন দিয়েছেন অনেক, অপর হাতে আবার কেড়েও নিয়েছেন অনেক। এ ছাড়া আরেকটা কথাও
আছে। বিধাতার কৃপায় মনুষ্যজীবন লাভ করা যায়; কিন্তু যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ
করতে হলে নিজ গুণে, নিজ সাধনাবলেই তা লাভ করতে হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে এ
সমস্তই পরিস্ফুট হবে। রবীন্দ্রনাথের জীবনটি পর্যালোচনা করে দেখলেই বোঝা
যাবে, তাঁর জীবনটি ঠিক কুসুমাকীর্ণ ছিল না, বরং কণ্টকাকীর্ণই বলতে হবে।
জীবনে শোক, তাপ, মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছেন প্রচুর। পত্নী এবং পরপর তিনটি
সন্তানকে হারিয়েছেন স্বল্পকাল মধ্যে। বৃহৎ পরিবার, পরম স্নেভাজন কনিষ্ঠরা
অনেকে চলে গিয়েছে অকালে, মনের অন্তস্তলে গভীর ক্ষতচিহ্ন রেখে। অপর দিকে
আবার নিকটতম আত্মীয়দের কাছেও আশানুরূপ ব্যবহার পাননি। বহু ব্যাপারে আপন
বিশ্বাসে অটল ছিলেন বলে জীবনে বন্ধুবিচ্ছেদও কিছু কম ঘটেনি। আদর্শবাদী
মানুষের জীবনে এ দুর্দৈব ঘটেই থাকে। বিশ্বখ্যাতি লাভের পরে অসূয়াবশত
দেশে-বিদেশে বেশ কিছু শত্রু লাভও হয়েছিল। বন্ধুজনের মুখেও বিষোদগার হয়েছে
প্রচুর। খ্যাতি-অখ্যাতি কোনোটাই তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি।
রবীন্দ্রনাথের
সহনশীলতা অত্যাশ্চর্য। ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি কখনো বড় করে দেখেননি। সমস্তই
অবিচলিত হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন। এত যে শোক-তাপ পেয়েছেন, তাও মুখ ফাটে কারও
কাছে এতটুকু মর্মবেদনা প্রকাশ করেননি। পুত্র-কন্যাদের মৃত্যুদিনেও
সাক্ষাৎকারীদের সঙ্গে এমন স্বাভাবিক এবং নির্বিকার চিত্তে কথাবার্তা বলেছেন
যে, শোকের বার্তা তাঁরা জানতেও পারেননি, বুঝতেও পারেননি। কঠিনতম দুঃখকেও
বিধাতার দান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কতখানি অবিচলিত হৃদয় হলে বলা সম্ভব, ‘এই
করেছ ভালো, নিষ্ঠুর হে, এই করেছে ভালো/এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন
জ্বালো।’ বলতে চেয়েছেন, জীবনবিধাতা আমাকে পরীক্ষা করে, যাচাই করে নিচ্ছেন।
এই যে আঘাতের পর আঘাত, এ বৃথা যাবে না, এর দ্বারা নিশ্চিত কোনো মহৎ
উদ্দেশ্য সাধিত হবে; হয়েছেও। দুঃখ একটা উদ্দীপনা। দুঃখের সকল অনুভূতি সজাগ
হয়ে ওঠে, দুঃখের আঘাতে সহনশীল মানুষের মনোবল শতগুণে বৃদ্ধি পায়।
ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতা বাড়ে, মনুষ্যত্বের মহিমা নিসংশয়রূপে প্রমাণিত হয়।
এই কথাটি বলেছেন অনুপম উপমা সহযোগে, ‘আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছু নাহি
ঢালে/আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছু আলো।’ মৃত্যুকে একটা অবিমিশ্র
অকল্যাণ হিসাবে দেখেননি; বিধাতার ইচ্ছার কাছে সর্বান্তকরণে আত্মসমর্পণ
করেছেন। বলেছেন, ‘দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে মঙ্গল আলোক/তবে তাই হোক।’ গভীর
প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন, ‘মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক/তবে তাই
হোক্।’
রবীন্দ্রসংগীতে যেমন মৃত্যু একটা মস্ত বড় দর্পণ, প্রেমও তেমনি।
মৃত্যু ঘটায় বিচ্ছেদ, প্রেম, মিলন। মৃত্যু যে মুহূর্তে এলো, সে মুহূর্তেই
সংসারের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটল। কিন্তু মজার কথা এই যে, দুই প্রেমিক যখন
প্রেমাসক্ত হলো তখন তাদের সঙ্গেও সংসারের বিচ্ছেদ ঘটল। দুজন একে অন্যকে
নিয়ে এত ব্যস্ত যে ‘সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব।’ অপর দিকে
আবার এই যে মৃত্যুর কথা এবং প্রেমের কথা এত করে বলেছেন তাতেই মিলনে
বিচ্ছেদে বেদনায় রচিত হয়েছে জীবনসংগীত। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কাব্যে
বৈষ্ণব কাব্যের প্রভাব অপরিসীম। বৈষ্ণব কবিরা, স্বর্গীয় প্রেম এবং পার্থিব
প্রেমকে মিশিয়ে ফেলেছেন, দেবতাকে প্রিয় করেছেন, প্রিয়কে দেবতা।
রবীন্দ্রসংগীতেও পূজা পর্যায় এবং প্রেম পর্যায়ের গানে বৈষম্য সব সময়ে খুব
সুস্পষ্ট নয়। রবীন্দ্রকাব্যের ওপরে উপনিষদের প্রভাব নিয়ে অনেক কথা বলা
হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু বলেছেন তাঁর কাব্যে উপনিষদ যতখানি, বৈষ্ণব
পদাবলী ততখানি। বৈষ্ণব পদাবলীতে যে প্রেমের আকূতি প্রকাশ পেয়েছে,
রবীন্দ্রনাথের বহু প্রেমের গানে প্রণয়ের সেই ধরনটি স্পষ্টত ধরা পড়েছে।
‘আমার একটা কথা বাঁশি জানে,’ ‘হৃদয়ের একূল ওকূল দু কূল ভেসে যায়,’ ‘আমার মন
মানে না, দিন রজনী,’ ‘মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে’ বা ‘একটু কেবল বসতে
দিয়ো কাছে’ বহু সংখ্যক গানের মধ্যে কয়টি মাত্র উল্লেখ করা গেল। ভাবে এবং
ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে এ সব গানের সাদৃশ্য সুপরিস্ফুট।
একদা যাকে
শখ করে বলেছেন জীবনদেবতা, জীবনের শেষ কাব্যে তাকে বলেছেন ছলনাময়ী ‘তোমার
সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনা জালে, হে ছলনাময়ী।’ মৃত্যুর
মুখোমুখি হয়ে কবি এখন সত্যের খুব কাছাকাছি। তাই বলে জীবনের নিন্দা করছেন
না, জীবনের বন্দনাই গাইছেন। নারীকে বলা হয়েছে ছলনাময়ী, সে কি নিন্দার কথা?
নারী যদি ছলনাময়ী না হতো, তাহলে সে ভালোবাসার অযোগ্য হতো। ছলনাময়ী নারী
হয়েছে মোহিনী মায়ায় অপরূপা। জীবনও তেমনি। বহু বাসনায় প্রাণপণের চেয়ে বঞ্চিত
হওয়ার মধ্যে রোমাঞ্চ আছে। রোমাঞ্চ এই কারণে যে সেখানেই মনুষ্যত্বের চরম
পরীক্ষা। বলেছেন, ‘এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্তের করেছ চিহ্নিত।’ জীবনের শেষ
বাক্যে জীবনের চরম সত্য উচ্চারিত হয়েছে ‘অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে/সে
পায় তোমার হাতে/শান্তির অক্ষয় অধিকার।’
রবীন্দ্রসংগীতের ভিতর দিয়ে
রবীন্দ্রজগতের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করা গেল। অবশ্য এ কথা কেউ যেন না ভাবেন
যে, রবীন্দ্রসংগীতের বাইরে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। মননশীল
ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কোথাও ঢাকা থাকে না। তিনি স্বপ্রকাশ। অগণিত প্রবন্ধে,
মন্দিরের ভাষণে, চিঠিপত্রে তো বটেই, এমনকি গল্পে, উপন্যাসে নাটকেও তাঁর
ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট। এ সবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচিন্তা,
সমাজচিন্তা, স্বদেশচিন্তা, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহিত্য চিন্তা সমস্তই সমভাবে
বিদ্যমান। তবে এ কথা বলব যে, রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে রবীন্দ্রজীবনদর্শন
যতখানি কেন্দ্রীভূত হয়ে ধরা দিয়েছে এমন আর কোথাও নয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে
গীতবিতানই রবীন্দ্র জীবনদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ রেফারেন্স টীকা গ্রন্থ।
