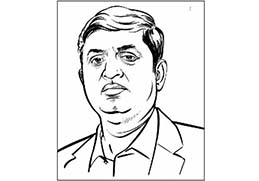
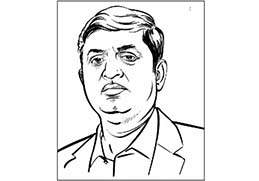
একটি নগরের
ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং তার সংরক্ষণ, শুধু নগরদর্শনের জন্যই নয়, বরং আগামী
প্রজন্মের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক প্রজন্মেরই তার নিজস্ব
কিছু স্থান থাকে, কিছু নিদর্শন থাকে, যা সদাপ্রবহমান সময়ে অমোঘ পদচিহ্ন
রেখে যায়। কিন্তু আজকের এ ঢাকায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্মৃতিকাতর বা
স্মৃতিবিধুর কোনো স্থান কি তৈরি করা সম্ভব? উল্লেখ্য, ঢাকায় খোলা জায়গা ও
প্রবেশযোগ্য পার্কের অভাব রয়েছে এবং একটি সমীক্ষা মতে, নগরের ৪০ শতাংশ
বাসিন্দা কখনো পার্কে যান না।
একটি নগর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয়,
নগরব্যবস্থা পরিপক্ব হয়ে ওঠে। নগরের সড়ক, স্থাপনা, উন্মুক্ত স্থানসহ
বিভিন্ন উপাদান সময়ের সাক্ষ্য বহন করে চলে। নগরের এই বৈশিষ্ট্যগুলোকেই তরুণ
প্রজন্ম বর্তমান হিসেবে আলিঙ্গন করে আর প্রবীণ প্রজন্ম এর মাঝে লালন করে
অতীতের স্মৃতি। পরিবর্তনশীল এই নগর এবং সমাজ একটি চক্রের মতো চিরন্তন ছন্দে
প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে হস্তান্তরিত হয়। রাজধানী ঢাকাও এর ব্যতিক্রম
নয়। মুঘল আমলে গণপরিসর ছিল মূলত বাজার, যা চক নামে পরিচিত ছিল। এ ছাড়া
গণপরিসর হিসেবে উদ্যান বা বাগানের পাশাপাশি স্বতঃস্ফূর্তভাবেও এ ধরনের
স্থান গড়ে উঠেছিল।
মহল্লাগুলোয় প্রায়ই সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা
সমাবেশ আয়োজিত হতো। কিংবদন্তি স্থপতি মাজহারুল ইসলামের বর্ণনা অনুসারে, এসব
মহল্লার নোড বা সংযোগস্থল বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় সভা আয়োজনের জন্য
জনপ্রিয় ছিল, যা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা পূরণের পাশাপাশি পারস্পরিক যোগাযোগ ও
মানবমিথস্ক্রিয়ার চাহিদাও পূরণ করত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই চর্চাগুলো
হারিয়ে গেছে, নতুন আঙ্গিক প্রতিস্থাপিত হয়েছে। বিগত দিনগুলোতে মূলত বাগান,
চক, মহল্লা বা সড়কের বিভিন্ন সংযোগস্থলই এ ধরনের কার্যকলাপের আয়োজনস্থল
হিসেবে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে ক্যাফে, রেস্টুরেন্ট এবং কফি শপগুলো
ক্রমপরিবর্তনশীল এ নগরের পুরোনো রীতি এবং স্থানগুলোর পরিপূরক হয়ে উঠেছে।
পরিবর্তিত
আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক আবহের মধ্যদিয়ে ঢাকার গণপরিসর বিভিন্ন রূপ ধারণ
করেছে। একসময় অসংখ্য ঐতিহ্যের আবাসস্থল ঢাকা, বর্তমানে নতুন সংস্কৃতি এবং
পরিবর্তিত সামাজিক প্রেক্ষাপট ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে নতুনভাবে
সংজ্ঞায়িত করছে, নতুন রূপ ধারণ করেছে। জাতিসংঘ প্রণীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট
(এসডিজি)-এর ১১ নম্বর অভীষ্ট হলো ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল
এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা।’ যার অন্যতম লক্ষ্যমাত্রা হলো ‘২০৩০
সালের মধ্যে সবার জন্য বিশেষ করে নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী মানুষের
জন্য নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অবারিত (প্রবেশাধিকারযুক্ত) সবুজ ও অন্য
উন্মুক্ত স্থানে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার প্রদান।’ এ ছাড়া একটি নগরে
স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় সবুজের পরিমাণ কমপক্ষে ২৫ শতাংশ
থাকার কথা থাকলেও ঢাকায় বর্তমানে এই সবুজের পরিমাণ মাত্র ৮ শতাংশ। ফলে
অত্যধিক কংক্রিটকরণের কারণে শহরটি ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা বৃদ্ধি অর্থাৎ
তাপীয় দ্বীপ প্রভাব অনুভব করছে।
নগর দৃষ্টিকোণ থেকে নাগরিকদের
জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে
নগরায়ণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পুনর্মূল্যায়ন করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। এরই
মাঝে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নগরের পার্ক ও খেলার মাঠগুলোকে
সংস্কারের জন্য সময়োপযোগী প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ঢাকার পার্ক এবং খেলার মাঠ
পুনরুজ্জীবিত করার এ যাত্রায় ভিত্তিস্থপতিরা সূচনালগ্ন থেকেই জনগণের সক্রিয়
অংশগ্রহণের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।
সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশীজন
সম্পৃক্তকরণ, সবার মতামত গ্রহণ এবং বিবেচনার গুরুত্ব অনুধাবন করে
সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পরিচালিত জনমত সমীক্ষা, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে
‘অংশগ্রহণমূলক দ্রুত মূল্যায়ন সভা (চজঅ)’ এবং মাইনক্রাফট গেমিং সফটওয়্যারের
মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে তাদের স্বপ্নের উদ্যানগুলোকে সরাসরি রূপদানের মতো
তিনটি মৌলিক কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রথমেই জরিপের মাধ্যমে পার্কের
অবস্থা, ব্যবহারের ধরনসহ পছন্দসই সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত
এবং ব্যবহারকারী ও এলাকাবাসীর মতামত সংগ্রহ করা হয়। ‘স্পাইডার ম্যাপ’
প্রণয়নের মাধ্যমে পার্ক-সম্পর্কিত নির্দিষ্ট চাহিদাগুলো চিহ্নিত করে
সম্ভাব্য সমাধানগুলো উন্মোচিত করা হয়।
সবার অন্তর্ভুক্তিতা
নিশ্চিতকরণে পিআরএ সভার মাধ্যমে বিভিন্ন অংশীজন তথা, বিভিন্ন সংস্থা,
প্রবীণ নাগরিক, ব্যবসায়ী, শিশু-কিশোর, ক্রীড়া সংগঠক, স্থানীয় বাসিন্দা এবং
বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ সবার অংশগ্রহণে একই টেবিলে আলোচনার ব্যবস্থা
গ্রহণ করা হয়। গুণগত মানসম্পন্ন আদর্শ পার্ক তৈরির উদ্দেশ্যে ওই সেশনের
মাধ্যমে পার্কসংলগ্ন কমিউনিটিগুলোর চাহিদা এবং ধারণাগুলোকে গ্রহণ করে একটি
‘ড্রিম ম্যাপ বা স্বপ্নচিত্র’ প্রস্তুত করা হয়।
সীমাবদ্ধতাগুলোকে
সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে সব পার্ক ও খেলার মাঠে নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের
জন্য এর বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করে নকশায়ন করা হয়েছে। পার্ক ও খেলার
মাঠগুলোয় জনগণের প্রবেশ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য
পরিকল্পিতভাবে জোনিং করা হয়েছে। প্রতিটি স্বতন্ত্র জোন বিভিন্ন খেলাধুলা,
ব্যবহারকারীর পছন্দ এবং তাদের কার্যকর চাহিদাগুলোকে পূরণ করার পাশাপাশি
বিদ্যমান নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা হ্রাস করে প্রত্যেকের জন্য একটি উপভোগ্য
অভিজ্ঞতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য একটি রূপান্তর হলো
খেলার মাঠের প্রান্তগুলোকে ‘ট্রানজিশন স্পেসে’ পরিণত করা। পার্কের
বেষ্টনীগুলো শুধু পার্কটিকে সীমাবদ্ধ করে না বরং একটি দৃষ্টিলব্ধ সংযোগও
তৈরি করে। পার্কের মুক্তমঞ্চগুলো বিভিন্ন উৎসব বা উপলক্ষে অনায়াসে উদ্যাপন
এবং সমাবেশের একটি আদর্শ কেন্দ্র।
নগরকে শিশুবান্ধব, জনবান্ধব,
সর্বোপরি পরিবেশবান্ধব করে গড়ে তোলার জন্য পার্ক ও খেলার মাঠ সংস্কার এবং
নির্মাণের পাশাপাশি শিশুদের জন্য আরও স্থান তৈরি (চষধপব গধশরহম) করতে হবে।
এই স্থানগুলো কানাগলি, রাস্তার পার্শ্বস্থ অংশ, যেকোনো জমির অংশ অথবা খাল
বা নদীর পাশে উন্মুক্ত জায়গা হতে পারে। সঠিক এবং ন্যূনতম উপকরণ ব্যবহারের
মাধ্যমে একটি স্থানকে শিশুদের খেলার জায়গায় রূপান্তরিত করা সম্ভব। যেমন,
একটি গাছ বা জলাধার/ নিম্নাঞ্চল (ধিঃবৎ ফবঢ়ৎবংংরড়হ ধৎবধ)-কে ঘিরেও শিশুদের
বিভিন্ন রকম ক্রিয়াকলাপের আয়োজন বা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্থানীয়
সরকারের মাধ্যমে অব্যবহৃত সরকারি বা ব্যক্তিগত জমি এবং স্কুল-কলেজের
মাঠগুলোর বহুবিধ ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে।
অর্থাৎ অব্যবহৃত এসব
জমির সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করে পাবলিক-প্রাইভেট
পার্টনারশিপ বা কমিউনিটি পার্টনারশিপের মাধ্যমে শিশুদের জন্য সদ্ব্যবহার
করা উচিত। এর পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময়ে অব্যবহৃত থাকা স্থানগুলোয় তাদের
প্রাপ্যতা অনুযায়ী সময়-নির্ধারিতভাবে (ঞরসব ঝঃরঢ়ঁষধঃবফ) শিশুদের জন্য
ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ প্রাপ্যতা অনুযায়ী দিনের নির্দিষ্ট সময়ে
ব্যবহার হতে পারে অথবা দীর্ঘ সময়ব্যাপীও (৫-১০ বছর) হতে পারে। অবশ্যই এ
ধরনের প্রক্রিয়ায় কমিউনিটিভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে করে
ব্যক্তিগত অব্যবহৃত জমি বা স্থানগুলো শিশুদের ব্যবহারের জন্য প্রদানে জমির
মালিকরা আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এভাবে এসব জমি, লাইব্রেরি, শরীরচর্চা কেন্দ্র,
খেলাধুলার জায়গা বা অন্যান্য মিশ্র শিক্ষার স্থান হিসেবে ব্যবহারে মানুষকে
প্রণোদিত করার সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে।
এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার
অগ্রণী ভূমিকা পালন করে সরকারি, প্রাতিষ্ঠানিক বা সংগঠন মালিকানাধীন
মিলনায়তন ও মাল্টিপারপাস হলগুলো কমিউনিটিভিত্তিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে
পারে। এ ছাড়া যেসব সামাজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্র বা কমিউনিটি সেন্টার বিভিন্ন
সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক দখলের শিকার হয়েছে, সেগুলোকে পুনরুদ্ধারে
ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কমিউনিটি সেন্টারভিত্তিক শিশুবান্ধব সাংস্কৃতিক
এবং সামাজিক বিনোদন কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটাতে সচেষ্ট হতে হবে। এসব জমি বা
স্থান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে যৌথ পরিচালন
ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমান নগর কাঠামোয় শিশুদের সুন্দর শৈশব
নিশ্চিতে এ ধরনের ব্যবহার সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখতে সক্ষম।
ঢাকার
উন্মুক্ত স্থানগুলো বিশেষ করে পার্ক ও খেলার মাঠগুলো কেবল শিশু-কিশোর এবং
নগরবাসীর বিনোদনের স্থানই নয় বরং এর পাশাপাশি নগরে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায়
রাখা নিশ্চিতে অন্যতম হাতিয়ার। পাশাপাশি এই হাতিয়ার ব্যবহারে, আন্দোলনের
মাধ্যমে নগরের পার্ক ও খেলার মাঠগুলোকে সংস্কারের জন্য সময়োপযোগী প্রচেষ্টা
এবং ঢাকার পার্ক এবং খেলার মাঠগুলোর সংস্কার নিশ্চিত করার কার্যক্রমটি
একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। নগরের সংস্কারকৃত পার্ক এবং খেলার মাঠগুলো
নগরবাসীর স্বপ্ন এবং আকাক্সক্ষার জীবন্ত প্রতিফলন হওয়ার পাশাপাশি তাদের
অন্তর্ভুক্তিতা, যূথবদ্ধ আশা এবং স্থায়ী সম্প্রীতির বাস্তব মূর্ত প্রতীক
হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।
লেখক: স্থপতি, সহসভাপতি, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)
